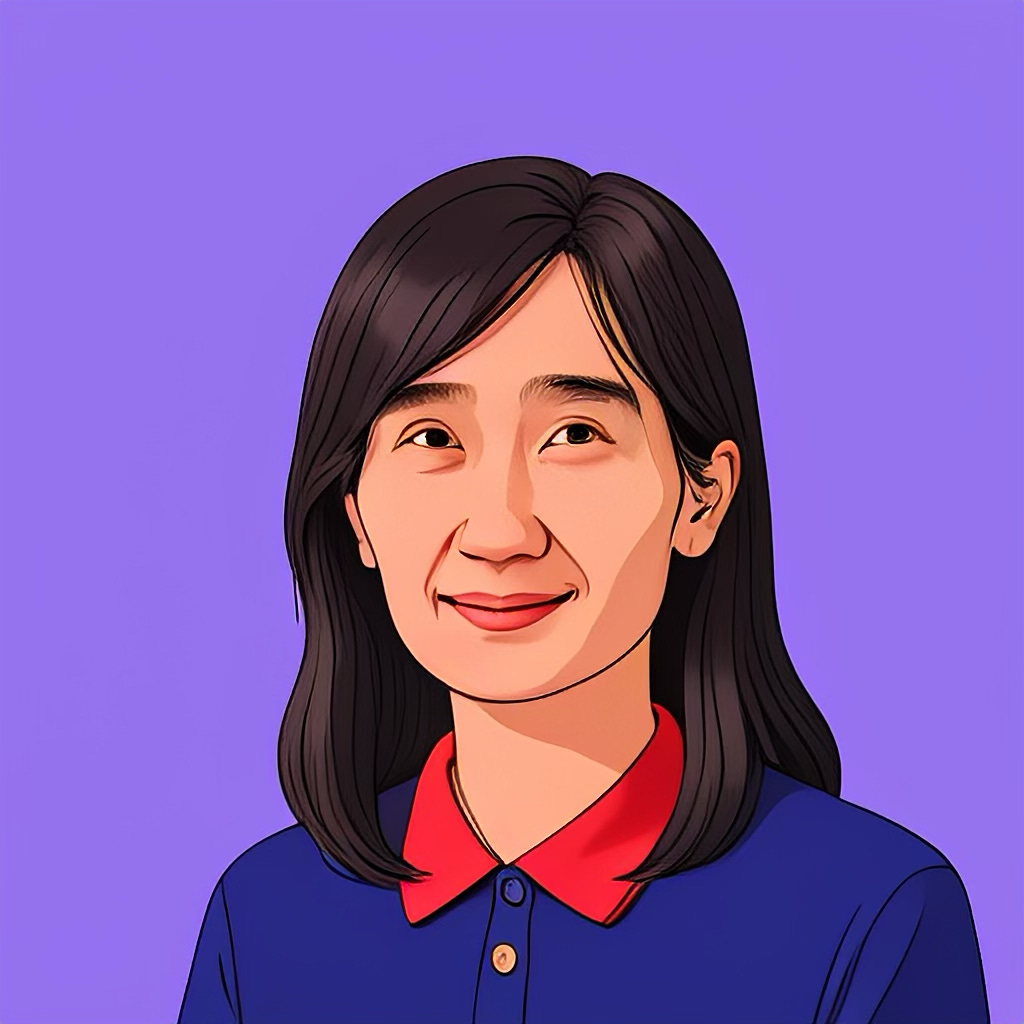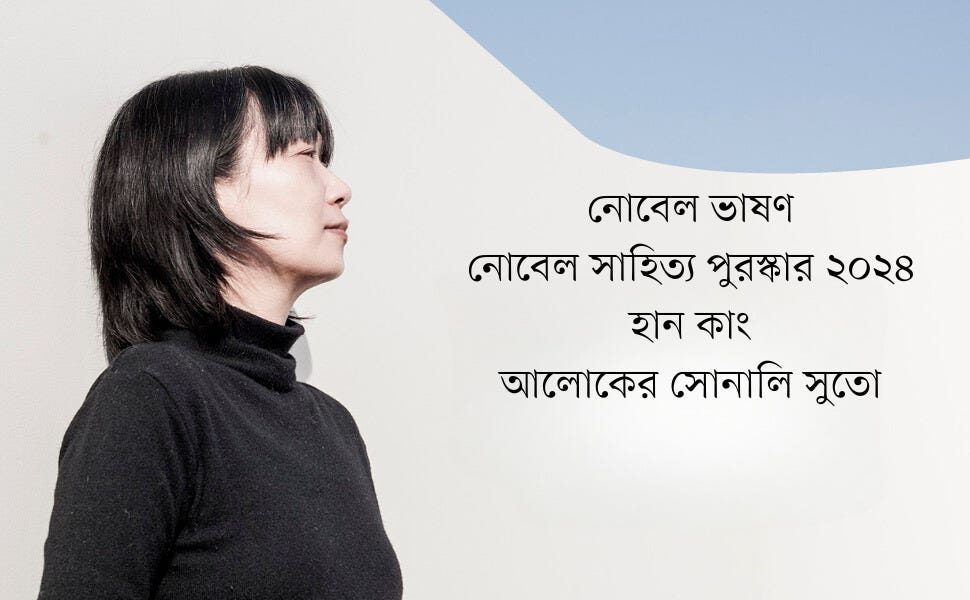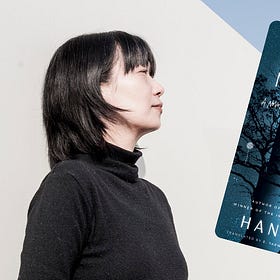হান কাং-এর নোবেল ভাষণ
যখন আমি একটি উপন্যাস নিয়ে কাজ করি, সেই প্রশ্নগুলোর স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিই। আমি তাদের ভেতরে বসবাস করি, তাদের গভীরে প্রবেশ করি।
নোবেল ভাষণ
নোবেল সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪
হান কাং
আলোকের সোনালি সুতো
গত জানুয়ারির বাসাবদলের সময় স্টোরেজরুমের কোণে পাওয়া গেল একটি পুরোনো জুতার বাক্স। খুলতেই অতীতের এক সুরভি ভরে দিল মনে—শৈশবের ডায়েরিগুলোর গন্ধ। বাক্সের ভেতর ছিল এক ছোট্ট পুস্তিকা, উপরে পেন্সিলে লেখা—“কবিতার বই।” পাঁচটি A5 কাগজ, মাঝখানে ভাঁজ করে স্ট্যাপলে বাঁধা। শিরোনামের নিচে আঁকা দুটি রেখা—একটি উঁচু ছয় ধাপে উঠেছে, অন্যটি নিচে সাত ধাপে নেমেছে। অলঙ্করণ না নিছক খেয়াল, বোঝা মুশকিল। পিছনে লেখা সাল—১৯৭৯—আর আমার নাম। পৃষ্ঠার ভাঁজে আটটি কবিতা, প্রতিটি ঝরঝরে পেন্সিলের ছোঁয়ায় লেখা। পাতার নিচে তারিখ, যেন স্মৃতির গাথা বুনেছে। শৈশবের সারল্যে ভরা আট বছরের কথাগুলো। তবে, এপ্রিলের একটি কবিতা যেন স্মৃতির নদীতে ঢেউ তোলে, আমাকে থমকে দেয়। কবিতার সেই প্রথম পঙ্ক্তিগুলো এমন—
ভালোবাসা কোথায়?
আমার বুকের ঢিপঢিপ শব্দে লুকিয়ে।
ভালোবাসা কী?
এটি সোনালি সুতো, যা হৃদয়ের ভেতর অদৃশ্য বাঁধনে জুড়ে দেয়।
এক মুহূর্তে আমি চল্লিশ বছর পেছনে চলে গেলাম। সেই বিকেলের স্মৃতি যেন ঝলমলিয়ে উঠল—যখন ছোট হাতে পুস্তিকাটি তৈরি করছিলাম। মোটা পেন্সিলের মাথায় বলপয়েন্টের ক্যাপ জড়ানো, ঘষামাজার ধুলোর সরু রেখা, আর বাবার ঘর থেকে চুরি করে আনা ভারী ধাতব স্ট্যাপলার—সবকিছু যেন চোখের সামনে জীবন্ত। মনে পড়ল, সিউলে যাওয়ার কথা শুনে কীভাবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কবিতাগুলো একত্র করব। নোটবইয়ের কোণ, ক্লাসের খাতার প্রান্ত, ডায়েরির ফাঁক থেকে তুলে এনে তাদের একটি বইয়ের রূপ দেব। কিন্তু সব সম্পূর্ণ হওয়ার পর, এই “কবিতার বই” যেন আমার শৈশবের গোপন মণিকোঠায় বন্দি হয়ে রইল। কারও দেখানোর ইচ্ছে হলো না। যেন শব্দে বোনা শৈশবের সুর একান্ত আমারই রয়ে গেল।
ডায়েরি আর পুস্তিকাটি যেমন পেয়েছিলাম, তেমন করেই গুছিয়ে রাখলাম। বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করার আগে ফোনে সেই কবিতাটির একটি ছবি তুলে নিলাম। মনে হলো, সেদিনের লেখা শব্দগুলোর সঙ্গে আজকের আমার এক অদৃশ্য সেতু জুড়ে রয়েছে। সেই সেতু, যা হৃদয়ের গভীরতম স্পন্দনে বাজে, যেন আমাদের বুকের ভেতর এক অলিখিত ভাষায় কথা বলে। সোনালি এক সুতো, যা সময়ের সীমা ছাড়িয়ে আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। একটি সুতো, যা আলো ছড়ায়, মায়ার মতো।
চৌদ্দ বছর পরে, প্রথম কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে আমি লেখার জগতে পা রাখলাম। পরের বছরই প্রকাশ পেল আমার প্রথম ছোটগল্প। এরপর আরও পাঁচ বছর পর, দীর্ঘ তিন বছরের প্রচেষ্টায় আমার প্রথম উপন্যাস আলোর মুখ দেখল। কবিতা ও ছোটগল্পের রচনাপ্রক্রিয়া আমাকে বরাবরই মোহিত করে, তবে উপন্যাস লেখার প্রতি আমার আকর্ষণ যেন আরও গভীর। আমার কিছু বই শেষ করতে লেগেছে এক বছর, আবার কিছুতে সাত বছর। এর বিনিময়ে আমার ব্যক্তিগত জীবনের বড় অংশ উৎসর্গ করতে হয়েছে। তবু, এই দীর্ঘ যাত্রাই আমাকে লেখার টেবিলে ফিরিয়ে আনে। সেই গভীরে প্রবেশের তীব্র বাসনা, যেখানে অনিবার্য প্রশ্নগুলোর মাঝে হারিয়ে যাওয়া যায়। এমন প্রশ্ন, যেগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য আমি জীবনের সঙ্গে সেই বিনিময়ের চুক্তি করতে রাজি হই।
প্রতিবার যখন আমি একটি উপন্যাস নিয়ে কাজ করি, সেই প্রশ্নগুলোর স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিই। আমি তাদের ভেতরে বসবাস করি, তাদের গভীরে প্রবেশ করি। এই প্রশ্নগুলোর শেষে পৌঁছানো মানে কখনোই তাদের উত্তর পাওয়া নয়, বরং লেখার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছানো যায়। তখন আমি আর আগের মতো থাকি না—এক নতুন আমি, বদলে যাওয়া এক অবস্থান থেকে আবার শুরু করি। পরবর্তী প্রশ্নগুলো যেন একে একে শিকলের কড়ির মতো যুক্ত হয়, অথবা ডোমিনোর মতো গড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি প্রশ্ন আমাকে নতুন কিছু লিখতে প্রেরণা দেয়, এক নতুন যাত্রায় এগিয়ে যেতে বলে।
২০০৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে যখন আমি আমার তৃতীয় উপন্যাস দ্য ভেজিটেরিয়ান লিখছিলাম, তখন কিছু জটিল ও তীব্র প্রশ্ন আমাকে গ্রাস করেছিল। একজন মানুষ কি সত্যিই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হতে পারে? আমরা কি সহিংসতাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে পারি? আর সেই মানুষ, যে স্বেচ্ছায় মানবজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তার ভাগ্যে কী ঘটে? এই প্রশ্নগুলো আমাকে প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি পৃষ্ঠায় ভাবিয়ে তুলেছিল।
সহিংসতাকে অস্বীকার করে মাংস খাওয়া ত্যাগ করা, এবং শেষে গাছ হয়ে ওঠার গভীর বিশ্বাসে ইয়ং-হাই নিজেকে এমন এক পরিহাসের মধ্যে ফেলে দেয়, যেখানে বাঁচার চেষ্টাই তাকে মৃত্যুর দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। ইয়ং-হাই এবং তার বোন ইন-হাই—যারা এই গল্পের সমান্তরাল নায়িকা—নিঃশব্দে তীব্র দুঃস্বপ্ন এবং ভেতরের ফাটলের ভেতর দিয়ে চলতে থাকে। তবুও, তারা একসঙ্গে। উপন্যাসের চূড়ান্ত দৃশ্যটি আমি একটি অ্যাম্বুলেন্সে স্থাপন করেছি। সেখানে আমি আশা করেছিলাম, ইয়ং-হাই এই গল্পের বাস্তবতায় জীবিত থাকবে। গাড়িটি সবুজ পাতার নিচে পাহাড়ি রাস্তায় দ্রুত নেমে যাচ্ছে, আর তার বোন ইন-হাই জানালার বাইরের দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে। হয়তো সে কোনো উত্তর খুঁজছে, কিংবা হয়তো সেই নিরবতার মধ্যেই এক অদৃশ্য প্রতিবাদ লুকিয়ে আছে।
এই উপন্যাস সম্পূর্ণই এক প্রশ্নমুখর অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে—তাকিয়ে থাকা আর প্রতিরোধের মাঝখানে, যেন কোনো প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায়।
দ্য ভেজিটেরিয়ান-এর পরবর্তী উপন্যাস ইঙ্ক অ্যান্ড ব্লাড এই প্রশ্নগুলোর গভীরতা আরও বাড়িয়ে তোলে। সহিংসতাকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে যদি জীবন আর পৃথিবীকেই অস্বীকার করতে হয়, তবে তা কতটা সম্ভব? আমরা তো গাছ হয়ে যেতে পারি না। তাহলে কীভাবে এই বিপরীতমুখী যাত্রা অব্যাহত রাখব? এই প্রশ্নের মধ্যেই যেন মানব অস্তিত্বের এক জটিল সুর প্রতিধ্বনিত হয়।
এই রহস্য উপন্যাসে রোমান ও ইতালিক অক্ষরে লেখা বাক্যগুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত, যেমন নায়িকা মৃত্যুর ছায়ার সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে প্রমাণ করতে চায় যে তার বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু আত্মহত্যা নয়। শেষ দৃশ্যটি লিখতে গিয়ে, যখন তাকে মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে ধ্বংস আর মৃত্যুর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি, তখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম: শেষ পর্যন্ত কি আমাদের বাঁচতেই হবে না? আমাদের জীবন কি সত্যের সাক্ষ্য বহন করতে পারবে না? এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই যেন জীবনের এক অনিবার্য প্রশ্ন মূর্ত হয়ে ওঠে।
আমার পঞ্চম উপন্যাস গ্রিক লেসনস-এ আমি এই প্রশ্নগুলোর আরও গভীরে প্রবেশ করেছি। যদি এই পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকতেই হয়, তবে কোন মুহূর্তগুলো সেই জীবনের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়? এক নারী, যিনি তার কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছেন, এবং এক পুরুষ, যিনি দৃষ্টিশক্তি হারানোর পথে, নীরবতা ও অন্ধকারের অজানা পথে হাঁটছেন। তাদের একাকী যাত্রাপথ একসময় এসে মিলে যায় এক বিন্দুতে, যেখানে জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়ার নীরব আকুতি প্রতিধ্বনিত হয়।
এই গল্পে আমি স্পর্শের ক্ষণগুলোকে ধারণ করতে চেয়েছিলাম। উপন্যাসটি ধীরলয়ে এগিয়ে চলে—নীরবতা আর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে—যখন সেই নারী হাত বাড়িয়ে পুরুষটির তালুতে কয়েকটি শব্দ লিখে দেন। সেই মুহূর্ত, যেন অনন্তকাল বিস্তৃত, তাদের কোমলতম দিককে প্রকাশ করে। এখানেই আমি নিজেকে একটাই প্রশ্ন করেছিলাম: মানবতার এই কোমলতম অনুভূতিগুলোকে স্পর্শ করে, সেই উষ্ণতার অনস্বীকার্য উপস্থিতি অনুভব করে, আমরা কি এই ক্ষণস্থায়ী, সহিংস পৃথিবীতে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে পেতে পারি?
২০১২ সালের বসন্তে, গ্রিক লেসনস প্রকাশের অল্প কিছুদিন পর, আমি যেন এই প্রশ্নগুলোর শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। তখন মনে হল, এবার এমন একটি উপন্যাস লিখব, যা আলো ও উষ্ণতার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। জীবনের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি গভীর ভালোবাসায় ভরা সেই বইটি হবে উজ্জ্বল, স্বচ্ছ অনুভূতির আলোকে ভাস্বর—একটি সৃষ্টির খোঁজ, যা আশা ও আলোর প্রতীক হয়ে উঠবে।
শীঘ্রই একটি শিরোনাম খুঁজে পেলাম এবং প্রথম খসড়ার কুড়ি পৃষ্ঠা লিখেও ফেললাম। কিন্তু হঠাৎ থেমে যেতে হলো। অনুভব করলাম, আমার ভেতরের কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন এই উপন্যাস লেখার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এমন কিছু, যা পুরোপুরি বোঝা না গেলেও, আমাকে থামতে বাধ্য করল।
তখনও গওয়াংজু নিয়ে লেখার কথা আমার ভাবনাতেও আসেনি।
১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে, আমি তখন মাত্র নয় বছর বয়সী, আমাদের পরিবার গওয়াংজু ছেড়ে চলে আসে—তার ঠিক চার মাস পর সেখানে ভয়াবহ গণহত্যা শুরু হয়। কয়েক বছর পর, একটি বইয়ের তাক থেকে উল্টে রাখা গওয়াংজু ফটো বুক আবিষ্কার করলাম। তখন আমার বয়স বারো। বড়দের চোখের আড়ালে বইটি পড়তে শুরু করলাম। পাতায় পাতায় ছিল গওয়াংজুর সেই সাহসী নাগরিক ও ছাত্রদের ছবি, যারা সামরিক অভ্যুত্থানের শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে গিয়ে লাঠি, বেয়নেট আর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। কঠোর সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ভেতর যখন সত্যকে চেপে দেওয়া হচ্ছিল, তখন বেঁচে থাকা মানুষ ও নিহতদের পরিবার এই বইটি গোপনে প্রকাশ ও বিতরণ করেছিলেন, যেন ইতিহাসের নীরব আর্তনাদ হারিয়ে না যায়।
শিশুবয়সে এই ছবিগুলোর রাজনৈতিক তাৎপর্য আমার বোধগম্য হয়নি। তবে বিধ্বস্ত সেই মুখগুলো আমার মনে এক অমোচনীয় প্রশ্ন হিসেবে গেঁথে যায়: একজন মানুষের পক্ষে কি অন্য মানুষের প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা সম্ভব? পরে, একটি ছবি—বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে রক্তদান করতে অপেক্ষায় থাকা মানুষের দীর্ঘ সারি—আমার মনে আরেকটি প্রশ্ন তোলে: একজন মানুষের পক্ষে কি অন্য মানুষের জন্য এমন আত্মত্যাগ সম্ভব? এই দুই বিপরীত প্রশ্ন যেন আমার চিন্তার জগতে গভীর ছাপ ফেলে।
এই দুটি প্রশ্ন আমার মনে ধাক্কা খেয়ে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের বৈপরীত্য এক অসামঞ্জস্যপূর্ণ গিঁটে পরিণত হয়, যা আমি কোনোভাবেই খুলতে পারছিলাম না।
তাই ২০১২ সালের বসন্তের এক দিনে, যখন আমি জীবনঘনিষ্ঠ একটি উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছিলাম, তখন আবারও সেই অমীমাংসিত সমস্যার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মানুষের প্রতি গভীর, প্রোথিত আস্থার অনুভূতি আমি বহু আগেই হারিয়েছি। তাহলে কীভাবে আমি এই পৃথিবীকে আলিঙ্গন করব? বুঝতে পারলাম, সামনে এগোতে হলে আমাকে এই অসম্ভব ধাঁধার মুখোমুখি হতেই হবে। উপলব্ধি করলাম, এই সমস্যার ভেতর দিয়ে যাওয়ার এবং তা অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হলো আমার লেখালেখি।
সেই বছরটির বেশিরভাগ সময় আমি আমার উপন্যাসের খসড়া তৈরি করতেই কাটিয়েছি, মনে মনে কল্পনা করছিলাম যে ১৯৮০ সালের মে মাসের গওয়াংজু বইটির একটি স্তর হিসেবে থাকবে। ডিসেম্বরের এক দিনে, আমি মাংওল-ডংয়ের কবরস্থানে গিয়েছিলাম। দুপুর গড়িয়ে গেছে, আর আগের দিনের ভারী তুষারপাতে চারপাশ ঢাকা। পরে, যখন আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল, সেই হিমশীতল কবরস্থান থেকে বুকে হাত রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। তখন নিজেকে বলেছিলাম, এই উপন্যাস গওয়াংজুকে শুধু একটি স্তরে সীমাবদ্ধ রাখবে না, বরং তার প্রতি সরাসরি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে।
এরপর আমি এমন একটি বই সংগ্রহ করলাম, যেখানে ৯০০-রও বেশি সাক্ষ্য ছিল। এক মাস ধরে প্রতিদিন নয় ঘণ্টা করে সেই সমস্ত সাক্ষ্য পড়ে গেছি। শুধু গওয়াংজুই নয়, রাষ্ট্রীয় সহিংসতার অন্যান্য ঘটনাও গভীর মনোযোগে খুঁজে দেখেছি। আরও পেছনে ফিরে, আরও বিস্তৃতভাবে তাকিয়ে, পড়েছি সেই গণহত্যাগুলোর কথা, যা মানুষ বারবার এই পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটিয়েছে। প্রতিটি পৃষ্ঠা যেন মানবতার এক করুণ প্রতিচ্ছবি।
উপন্যাসের জন্য গবেষণার সেই সময়ে, দুটি প্রশ্ন যেন ছায়ার মতো আমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করত। পঁচিশে পা দেওয়ার পর থেকে প্রতিটি নতুন ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠায় এই পঙ্ক্তিগুলো আমি লিখে রাখতাম:
বর্তমান কি পৌঁছায় অতীতের গভীরে?
জীবিতেরা কি মৃতদের স্পর্শে বাঁচাতে পারে?
গবেষণার প্রতিটি দিনে উপলব্ধি করছিলাম, এই প্রশ্নগুলো আসলে অসম্ভবের মুখোমুখি। মানবতার সবচেয়ে অন্ধকার দিকগুলোর সঙ্গে এই গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি সংঘর্ষ আমার বিশ্বাসের শেষ অবশিষ্টটুকুকেও ভেঙে চুরমার করে দিল। উপন্যাসটি প্রায় ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।
ঠিক তখনই পড়লাম এক তরুণ রাত্রিকালীন স্কুল শিক্ষকের ডায়েরি। লাজুক, শান্ত স্বভাবের সেই যুবক, পার্ক ইয়ং-জুন, ১৯৮০ সালের মে মাসে গওয়াংজুর দশ দিনের বিদ্রোহে গড়ে ওঠা দলের অংশ ছিলেন। প্রাদেশিক প্রশাসন ভবনের কাছে YWCA ভবনে তিনি থেকে গিয়েছিলেন, যদিও জানতেন ভোরেই সৈন্যরা ফিরে আসবে। সেখানেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ডায়েরির প্রতিটি পৃষ্ঠা যেন এক তীব্র নীরব আর্তনাদ।
শেষ রাতে, নিজের ডায়েরিতে পার্ক ইয়ং-জুন লিখেছিলেন, “হে ঈশ্বর, কেন আমার বিবেক এত তীব্রভাবে আমাকে বিদ্ধ করে? আমি বাঁচতে চাই।” এই লাইনগুলো পড়ে যেন বজ্রাঘাতের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল, আমার উপন্যাস কোন পথে এগোবে। বুঝতে পারলাম, আমার সেই দুটি প্রশ্নকে উল্টে দিতে হবে:
অতীত কি বর্তমানকে সাহায্য করতে পারে?
মৃতেরা কি জীবিতদের রক্ষা করতে পারে?
পরে, যখন আমি হিউম্যান অ্যাক্টস লিখছিলাম, কিছু মুহূর্তে অনুভব করতাম, সত্যিই যেন অতীত বর্তমানকে সাহায্য করছে, আর মৃতেরা জীবিতদের রক্ষা করছে। এমন অনুভূতিতে লেখা এগিয়ে চলত, যেন প্রতিটি শব্দের ভেতর দিয়ে ইতিহাসের স্পর্শ জেগে উঠছে। মাঝে মাঝে আমি কবরস্থানে ফিরে যেতাম, আর প্রতিবারই আশ্চর্যজনকভাবে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকত। চোখ বন্ধ করলে সূর্যের কমলা রশ্মি যেন আমার চোখের পাতা ভেদ করে হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যেত, এক নীরব উষ্ণতার মতো।
তখন সেই আলোকে জীবনের নিজস্ব আলো বলে মনে হতো। বাতাস আর আলো আমাকে এমন এক উষ্ণতায় জড়িয়ে রাখত, যা কোনো ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।
সেই ছবির বই দেখার অনেক দিন পরেও আমার মনে রয়ে গিয়েছিল এই প্রশ্নগুলো:
কীভাবে মানুষ এতটা নিষ্ঠুর আর সহিংস হতে পারে? অথচ একইসঙ্গে কীভাবে তারা এই অসীম সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারে? মানুষ নামক প্রজাতির অংশ হওয়ার অর্থ আসলে কী?
মানবতার ভয়াবহতা আর মর্যাদার এই দুই প্রান্তের মাঝখানের শূন্যতায়, এক অসম্ভব পথ নির্মাণের জন্য, আমার প্রয়োজন ছিল মৃতদের সহায়তা। যেমন হিউম্যান অ্যাক্টস উপন্যাসে, যেখানে শিশু ডং-হো তার মায়ের হাত ধরে সূর্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়।
অবশ্যই, যা মৃতদের, শোকাহতদের, বা বেঁচে থাকা মানুষদের ওপর ঘটেছে, তা ফিরিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি কেবল তাদের দিতে পারতাম আমার হৃদয়ে বয়ে চলা অনুভূতি, আবেগ, আর জীবনের স্পন্দন।
উপন্যাসের শুরু ও শেষে একটি মোমবাতির আলো জ্বালানোর ভাবনা নিয়ে, আমি প্রথম দৃশ্যটি স্থাপন করেছিলাম পৌর জিমনেসিয়ামে—যেখানে মৃতদেহগুলো রাখা হয়েছিল এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। সেখানেই দেখি, পনেরো বছরের ডং-হো সাদা চাদর বিছিয়ে মৃতদেহগুলোর উপর মোমবাতি জ্বালাচ্ছে। প্রতিটি শিখার ফ্যাকাশে নীল হৃদয়ে সে গভীরভাবে তাকিয়ে আছে, যেন মোমের আলোয় মৃতদের স্পর্শ করার এক নীরব প্রয়াস।
এই উপন্যাসের কোরিয়ান শিরোনাম Sonyeon-i Onda, যার শেষ শব্দ onda ক্রিয়াপদ oda, অর্থাৎ ‘আসা’-র বর্তমান কাল। যখন সেই sonyeon, সেই কিশোর, দ্বিতীয় পুরুষে ‘তুমি’ বলে সম্বোধিত হয়—অন্তরঙ্গতায় হোক বা দূরত্বপূর্ণভাবে—সে ম্লান আলোয় জেগে ওঠে এবং বর্তমানের দিকে হাঁটতে শুরু করে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন এক আত্মার পদচিহ্ন।
সে ধীরে ধীরে কাছে আসে এবং বর্তমানে মিশে যায়। যখন মানবিক নিষ্ঠুরতা এবং মর্যাদা সমান্তরাল চরমে সহাবস্থান করে, সেই সময় এবং স্থানকে যদি ‘গওয়াংজু’ নামে ডাকা হয়, তখন সেই নাম আর কেবল একটি শহরের সুনির্দিষ্ট নাম থাকে না। তা রূপান্তরিত হয় একটি সাধারণ নাম হিসেবে, যেমনটা আমি এই বইটি লিখতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি।
গওয়াংজু বারবার ফিরে আসে—সময় আর স্থানের সীমা অতিক্রম করে, এবং সর্বদা বর্তমান কালেই। এমনকি এখনও।
২০১৪ সালের বসন্তে যখন বইটি শেষমেশ প্রকাশিত হলো, পাঠকেরা বইটি পড়ে যে যন্ত্রণার কথা জানালেন, তা আমাকে অবাক করল। লেখার পুরো সময়জুড়ে যে ব্যথা আমি অনুভব করেছিলাম এবং পাঠকেরা যে অশান্তির কথা বলছিলেন, সেগুলোর মধ্যে সংযোগ খুঁজে পেতে আমাকে কিছু সময় নিতে হলো।
এই যন্ত্রণা আসলে কী বোঝায়? আমরা কি মানবতার ওপর আস্থা রাখতে চাই, আর সেই আস্থা টলে গেলে মনে হয় আমাদের অস্তিত্বই যেন ভেঙে পড়ছে? আমরা কি মানবতাকে ভালোবাসতে চাই, আর সেই ভালোবাসা ভেঙে গেলে এই ব্যথাই কি আমাদের গভীরে বিদ্ধ করে?
তবে কি ভালোবাসা থেকে ব্যথার জন্ম হয়? আর কিছু ব্যথা কি ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে?
সেই বছর, জুনের এক রাতে, স্বপ্নে দেখলাম—বিশাল এক প্রান্তর, হালকা তুষারে ঢাকা। প্রান্তরে ছড়িয়ে কালো গাছের গোড়া, প্রতিটির পেছনে কবরের ঢিবি। হাঁটতে হাঁটতে টের পেলাম, আমি হাঁটছি পানির উপর। পেছনে ফিরে দেখি, প্রান্তরের কিনারা, যা দিগন্ত ভেবেছিলাম, সেখান থেকে সমুদ্র এগিয়ে আসছে।
ভাবলাম, এমন স্থানে কবর কেন? সমুদ্রের স্রোতে ঢিবিগুলো কি ভেসে যাবে না? অন্তত ওপরের ঢিবির হাড়গুলো সরিয়ে নেওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ সময় আছে? কিন্তু কীভাবে? আমার কাছে তো এমনকি একটি কোদালও নেই।
জল তখন আমার গোড়ালি পর্যন্ত উঠে এসেছে। ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার জানালার দিকে তাকিয়ে অনুভব করলাম, এই স্বপ্ন যেন আমাকে কিছু গভীর কথা বলছে। স্বপ্নটি লিখে রাখার পর মনে হলো, হয়তো এটাই হবে আমার পরবর্তী উপন্যাসের সূচনা।
তবে জানতাম না, সেই স্বপ্ন থেকে গল্প কোন দিকে যাবে। কয়েকটি সম্ভাব্য গল্প শুরু করেছিলাম, আবার বাতিল করেছি। শেষ পর্যন্ত, ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে, জেজু দ্বীপে একটি ঘর ভাড়া নিলাম। পরবর্তী দুই বছর ভাগ করে কাটালাম জেজু আর সিউলের মধ্যে।
জঙ্গল, সমুদ্রের তীর, গ্রাম্য পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে, জেজুর তীব্র প্রকৃতিকে প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করলাম—তার হাওয়া, আলো, তুষার আর বৃষ্টি। এই প্রকৃতির ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে উপন্যাসটির রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। হিউম্যান অ্যাক্টস-এর মতো এখানেও আমি গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষের সাক্ষ্য পড়লাম, গবেষণার প্রতিটি উপাদান গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। নির্মম অথচ অপ্রকাশযোগ্য তথ্যের দিকে চোখ সরিয়ে না রেখে সংযমী ভঙ্গিতে লিখতে শুরু করলাম। এই লেখাগুলোই পরিণত হলো We Do Not Part-এ, যা প্রকাশিত হয় সেই স্বপ্নের সাত বছর পর—যেখানে আমি কালো গাছের গোড়া আর গর্জে ওঠা সমুদ্র দেখেছিলাম।
সেই বইয়ের জন্য রাখা নোটবুকে আমি লিখেছিলাম:
জীবন চায় বাঁচতে। জীবন উষ্ণ, তপ্ত।
মৃত্যু মানে শীতলতায় জমে যাওয়া—তুষার মুখে জমে থাকা, কখনো গলে না।
হত্যা মানে উষ্ণতাকে কেড়ে নিয়ে ঠান্ডায় পরিণত করা।
মানুষ, ইতিহাসের মধ্যে, আর মানুষ, মহাবিশ্বের বুকে।
বাতাসের স্রোত, সমুদ্রের ঢেউ—জল আর হাওয়ার চক্রাকার প্রবাহ, যা গোটা পৃথিবীকে একসূত্রে বাঁধে।
আমরা জড়িত, একে অপরের সঙ্গে। আমি প্রার্থনা করি—এই বন্ধন যেন থাকে, চিরকাল।
উপন্যাসটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি অনুভূমিক যাত্রার গল্প, যেখানে কথক কিউংহা একটি পোষা পাখিকে বাঁচানোর সিউল থেকে ভারী তুষারের মধ্য দিয়ে জেজুর উপত্যকায় তার বন্ধু ইনসনের বাড়ি পৌঁছায়।
দ্বিতীয় অংশে যাত্রাটি ঊর্ধ্বাধভাবে অবস্থিত—কিউংহা এবং ইনসন মানবতার সবচেয়ে অন্ধকার রাত্রির দিকে নেমে যায়। ১৯৪৮ সালের শীতকাল, যখন জেজুর সাধারণ মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছিল, তারা সেই স্মৃতির গভীরে ডুবে যায় এবং শেষ পর্যন্ত গভীর সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে যায়।
তৃতীয় এবং শেষ অংশে, তারা দুজন সমুদ্রের তলায় একটি মোমবাতি জ্বালায়।
যদিও উপন্যাসটি দুই বন্ধুর যাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলে, যেমন তারা পালা করে মোমবাতি ধরে রাখে, এর প্রকৃত নায়িকা হলেন ইনসনের মা, জংসিম। যিনি জেজুর গণহত্যা থেকে বেঁচে থেকেও ভালোবাসার মানুষের একটি হাড়ের টুকরো খুঁজে বের করার জন্য লড়াই করেছেন, যাতে তিনি সঠিকভাবে শেষকৃত্য করতে পারেন। সেই জংসিম, যিনি শোককে থামতে দেননি, যিনি যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে বিস্মৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। যিনি বিদায় জানান না।
তার জীবনের দিকে তাকিয়ে—যে জীবন দীর্ঘকাল ধরে সমানভাবে ভালোবাসা ও যন্ত্রণায় ফুঁসছিল—আমার মনে হয়, আমি নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করছিলাম:
আমরা কতটা ভালোবাসতে পারি? আমাদের সীমা কোথায়?
মানবিক থাকতে হলে শেষ পর্যন্ত কতটা ভালোবাসা আমাদের প্রয়োজন?
We Do Not Part-এর কোরিয়ান সংস্করণ প্রকাশের তিন বছর পরেও আমার পরবর্তী উপন্যাসটি অসমাপ্ত। আর যে বইটি আমি ভেবেছিলাম এর পরে লিখব, সেটিও দীর্ঘদিন ধরে আমাকে অপেক্ষায় রেখেছে। সেই উপন্যাসটি দ্য হোয়াইট বুক-এর সঙ্গে আঙ্গিকগতভাবে যুক্ত—একটি বই, যা আমি লিখেছিলাম আমার বড় বোনের জন্য, যিনি জন্মের দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিলেন। আমি চেয়েছিলাম কিছু সময়ের জন্য আমার জীবন তাকে ধার দিতে এবং সেই অংশগুলোর দিকে তাকাতে, যা কোনো পরিস্থিতিতেই ধ্বংস হয় না।
সব সময়ের মতোই, কখন কি সম্পূর্ণ হবে তা অনুমান করা অসম্ভব। তবে আমি লিখে যাব, যত ধীর গতিতেই হোক না কেন। আমি পেছনে ফেলে আসব ইতোমধ্যে লেখা বইগুলোকে এবং এগিয়ে চলব, যতক্ষণ না কোনো মোড় ঘুরে তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে দেখতে পাই। যতদূর আমার জীবন আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
যখন আমি আমার বইগুলো থেকে দূরে সরে যাব, তারা আমার থেকে স্বাধীন হয়ে তাদের নিজস্ব জীবনের পথে এগিয়ে চলবে, নিজেদের ভাগ্য অনুসারে। যেমন একসঙ্গে থাকবে সেই দুই বোন, চিরকাল, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে, আর সামনের কাচের বাইরে সবুজ আগুনের দহন। যেমন সেই নারী, শীঘ্রই যিনি তার কথা ফিরে পাবেন, অন্ধকারে, নীরবতায়, পুরুষটির তালুতে আঙুল দিয়ে লিখবেন। যেমন আমার বোন, যিনি এই পৃথিবীতে মাত্র দুই ঘণ্টার জন্য এসেছিলেন, আর আমার তরুণ মা, যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার শিশুকে অনুরোধ করেছিলেন, “মরো না, দয়া করে মরো না।”
এই আত্মাগুলো কতদূর যাবে—যারা আমার চোখের পাতা বন্ধের আড়ালে গাঢ় কমলা আলোয় মিশে গিয়েছিল, যারা আমাকে সেই অকথ্য উষ্ণ আলোর আচ্ছাদনে মুড়ে নিয়েছিল?
কতদূর ভ্রমণ করবে সেই মোমবাতিগুলো—যেগুলো জ্বালানো হয়েছিল প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের স্থানে, প্রতিটি সময় ও স্থানে, যা অবর্ণনীয় সহিংসতায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? যেগুলো হাতে তুলে নিয়েছিলেন তারা, যারা শপথ করেছিলেন কখনো বিদায় বলবেন না।
সেগুলো কি শিখা থেকে শিখায়, হৃদয় থেকে হৃদয়ে, সোনালি সুতোর ওপর ভেসে চলবে?
পুরোনো জুতার বাক্স থেকে গত জানুয়ারিতে উদ্ধার করা সেই পুস্তিকায়, ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে লেখা আমার অতীতের সেই নিজস্ব প্রশ্ন ছিল:
ভালোবাসা কোথায়?
ভালোবাসা কী?
অথচ, ২০২১ সালের শরৎ পর্যন্ত, যখন We Do Not Part প্রকাশিত হলো, আমার মনের গভীরে থাকা দুটি প্রধান প্রশ্ন ছিল এই:
পৃথিবী এত সহিংস আর বেদনাময় কেন?
তবু, কীভাবে পৃথিবী এতটা সুন্দর হতে পারে?
অনেক দিন ধরে আমি বিশ্বাস করতাম, এই বাক্যগুলোর মধ্যে থাকা টানাপোড়েন এবং অন্তর্দ্বন্দ্বই আমার লেখার মূল চালিকা শক্তি। আমার প্রথম উপন্যাস থেকে শুরু করে সর্বশেষটি পর্যন্ত, আমি যে প্রশ্নগুলোকে মনে রেখে লিখে এসেছি, সেগুলো সময়ের সঙ্গে বদলেছে এবং বিকশিত হয়েছে। তবে এই দুটি প্রশ্নই সবসময় অপরিবর্তিত থেকেছে।
কিন্তু দুই-তিন বছর আগে, আমার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। আমি কি সত্যিই ভালোবাসা নিয়ে, সেই যন্ত্রণার মূলসূত্র নিয়ে—যা আমাদের একত্রিত করে—শুধু ২০১৪ সালের বসন্তে হিউম্যান অ্যাক্টস প্রকাশের পর থেকেই ভাবতে শুরু করেছি? আমার প্রথম উপন্যাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, কি গভীরতম স্তরে আমার অনুসন্ধান সবসময়ই ভালোবাসার দিকেই নির্দেশ করেনি?
এমন কি হতে পারে যে ভালোবাসাই আমার জীবনের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে মৌলিক সুর?
১৯৭৯ সালের এপ্রিলে শিশুটি লিখেছিল, ভালোবাসা অবস্থান করে এক ব্যক্তিগত স্থানে, যাকে সে বলেছে ‘আমার হৃদয়’। (এটি আমার ঢিপঢিপ ধুকপুক করা বুকে লুকিয়ে আছে।)
আর ভালোবাসা কী, সেই প্রশ্নে তার উত্তর ছিল এমন: (এটি সোনালি সুতো, যা আমাদের হৃদয়গুলোকে একত্রে জুড়ে রাখে।)
আমি লিখি আমার শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে—দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, স্বাদ গ্রহণ, কোমলতা ও উষ্ণতার স্পর্শ, শীত আর ব্যথার অনুভূতি দিয়ে। আমি খেয়াল করি আমার হৃদয়ের ধুকপুকানি, শরীরের খাবার আর পানির প্রয়োজন, হাঁটা-দৌড়ানো, ত্বকের উপর দিয়ে বাতাস, বৃষ্টি, আর তুষারের ছোঁয়া, হাত ধরে রাখার অনুভূতি।
এই জাগ্রত অনুভূতিগুলো, যা আমার রক্তধারায় প্রবাহিত একটি মর্ত্যের অস্তিত্বের অংশ, আমি চেষ্টা করি সেগুলো আমার বাক্যে প্রবাহিত করতে। যেন প্রতিটি বাক্য বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো প্রেরিত হয়।
আর যখন আমি অনুভব করি এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ পাঠকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, তখন আমি বিস্মিত হই, আবেগে আপ্লুত হই। সেই মুহূর্তগুলোতে আমি আবার অনুভব করি সেই ভাষার সুতোর স্পর্শ, যা আমাদের একত্রে বেঁধে রাখে—কীভাবে আমার প্রশ্নগুলো সেই জীবন্ত, বৈদ্যুতিক সত্তার মাধ্যমে পাঠকদের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে।
যারা এই সুতোর মাধ্যমে আমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন, তাদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আর যারা ভবিষ্যতে এই সংযোগে অংশ নেবেন, তাদের প্রতিও।
ইংরেজি অনুবাদ: ই. ইয়েওন ও পেইজ আনিয়া মরিস
বাংলা অনুবাদ: রিটন খান