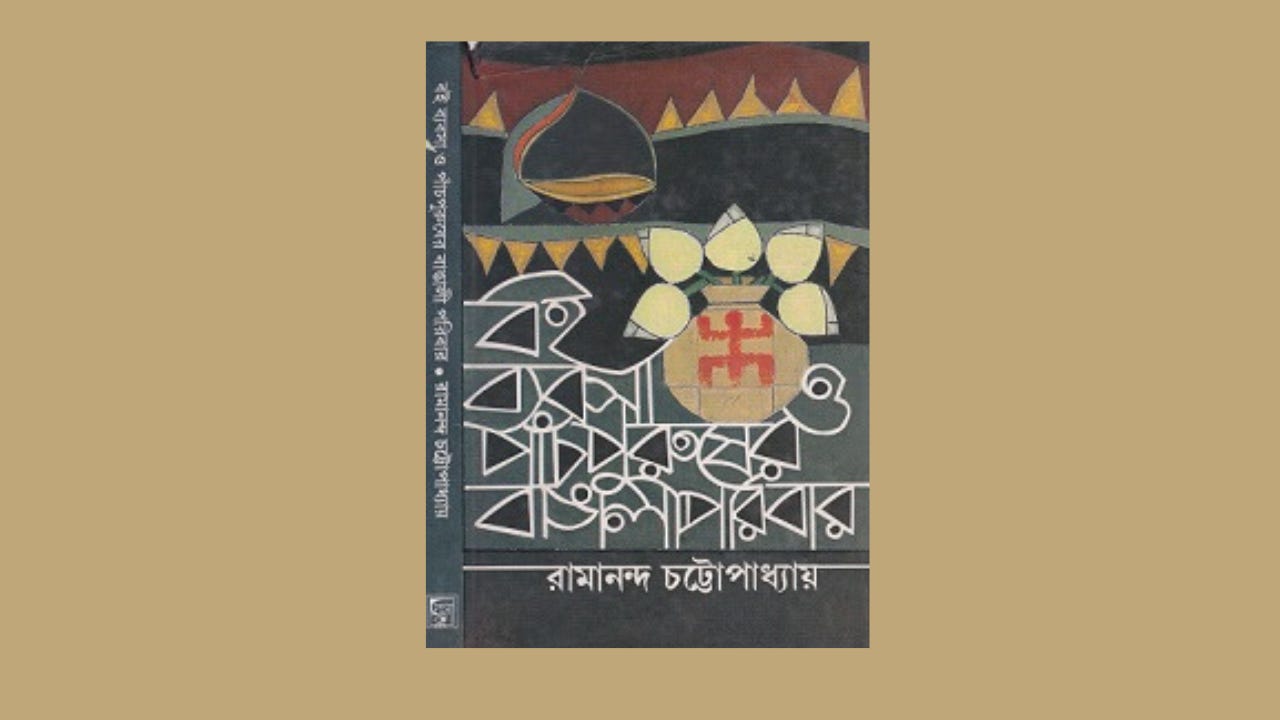শোভারাম দে মজুমদার: এক জীবন, এক সংগ্রাম
১৮৬০ সালে হাওড়ার পাতিহাল ছেড়ে বরদাপ্রসাদ মজুমদার কলকাতায় এলেন—জমিদারি ছেড়ে বইয়ের ব্যবসায় নামলেন। সেই যাত্রাই রচনা করল এক দীর্ঘ ইতিহাস, যা আজও বহন করে চলেছে তাঁর উত্তরসূরিরা—
বাঙালির ব্যবসা কি তিন পুরুষে শেষ?—প্রবাদবাক্যের মতো এই ধারণা আমাদের বিশ্বাসের গভীরে প্রোথিত। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে, যা প্রশ্ন তোলে—তারা কি সত্যিই বাঙালি? এমনই এক ব্যতিক্রমের দলিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থ “বই ব্যবসা ও পাঁচ প্রজন্মের বাঙালি পরিবার”। যেখানে তিনি তুলে ধরেছেন এক পুরোদস্তুর বাঙালি পরিবারের পাঁচ প্রজন্মব্যাপী ব্যবসায়িক সাফল্যের কাহিনি।
গ্রন্থটি মূলত দেব সাহিত্য কুটীর-এর ইতিহাস, যা ১৮৬০ সালে বরদাপ্রসাদ মজুমদারের হাত ধরে শুরু হয়েছিল কলকাতায়। বাংলা মুদ্রণের তখনও শতবর্ষ পূর্ণ হয়নি, অথচ এই প্রতিষ্ঠান নিরন্তর পরিশ্রম ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে ধাপে ধাপে বিকাশ লাভ করে। কোন বই, কাদের জন্য, কীভাবে ছাপা হবে—এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজতে গিয়ে তারা গড়ে তুলেছে টেকসই ব্যবসায়িক দর্শন। প্রযুক্তির পরিবর্তনকে স্বীকার করে এগোনোর কারণেই প্রতিষ্ঠানটি স্থবির হয়ে পড়েনি। দেব সাহিত্য কুটীর-এ সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বিরোধ দূর করে এক অনন্য সংমিশ্রণ ঘটেছে, যেখানে শিল্প ও বাণিজ্য পরস্পরকে সমৃদ্ধ করেছে।
বই ব্যবসা ধীরগতির, এখানে লাভের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রকাশনায় বিনিয়োগ জরুরি, নতুবা প্রতিষ্ঠান স্থবির হয়ে পড়ে। বরদাপ্রসাদের উত্তরসূরিরা এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছেন আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে। এ কারণেই দেব সাহিত্য কুটীর কেবল টিকে থাকেনি, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্মের পাঠককে আকৃষ্ট করতে পেরেছে।
১৮৬০ সালে হাওড়ার পাতিহাল ছেড়ে বরদাপ্রসাদ মজুমদার কলকাতায় এলেন—জমিদারি ছেড়ে বইয়ের ব্যবসায় নামলেন। সেই যাত্রাই রচনা করল এক দীর্ঘ ইতিহাস, যা আজও বহন করে চলেছে তাঁর উত্তরসূরিরা—কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই পেরিয়ে।
প্রেস, প্রকাশনা, অভিধান, পূজাবার্ষিকী, উপন্যাস, গল্প, নাটক, শুকতারা, নবকল্লোল—এইসবের সমৃদ্ধ ভান্ডার গড়ে উঠল, যা শুধুই ব্যবসা নয়, এক আনন্দের হাট। এমন বিরল প্রতিষ্ঠান দেড়শো বছর পার করছে, আর সেই ধারাবাহিকতার ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন গবেষক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—নির্ভীক ও নির্মোহ দৃষ্টিতে।
গ্রন্থটির পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে এই ঐতিহাসিক পথের আদ্যন্ত বিবরণ। দলিল-দস্তাবেজ, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র, প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকার—এইসব দুর্লভ উপাদানের আলোয় প্রতিষ্ঠানটির শিকড় ও বিকাশ অনবদ্য নৈপুণ্যে তুলে ধরা হয়েছে।
লেখক বইটির শেষ অংশে জ্যোতিভূষণ চাকী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যালসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার সংযোজন করেছেন, যেখানে উঠে এসেছে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা। পাশাপাশি দলিল, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্রের সাহায্যে তথ্যসমৃদ্ধ ও পরিশীলিত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন, যা আবেগে ভেসে যায়নি, বরং এক সুসংগঠিত ইতিহাস রচনা করেছে।
বইটির প্রাসঙ্গিকতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ—বাঙালির প্রকাশনাজগতের ইতিহাস বোঝার জন্য। তবে, একটি বিস্তৃত বংশপঞ্জি থাকলে তথ্যসমূহ আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারত। তবু, এটি বাংলা প্রকাশনা ব্যবসায় টিকে থাকার লড়াই ও সাফল্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।
শোভারামের জীবন ও সংগ্রাম
এক বিস্তৃত হলঘর, সিলিং জুড়ে ঝুলছে মখমলের চাঁদোয়া। দেওয়ালের দুই পাশে মুখোমুখি বাঁধানো দু’টি বিশাল তৈলচিত্র—সম্ভবত পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি। মেঝেতে কারুকাজ করা তক্তপোশের ওপর কিংখাব মোড়া গদিতে বসে আছেন ফৌজদার, পিছনে লম্বা তাকিয়া, পাশে পাশবালিশ। হাতে সোনায় বাঁধানো রুপোর গড়গড়া, সামনে হাতির দাঁতের বাক্স, দোয়াত-কলমদান, সীলমোহর, রুপোর পানদান, আর তক্তার নিচে রঙিন চীনামাটির পিকদানি।
ডানদিকে সম্ভ্রান্তদের জন্য কুর্শি ও ঝালর দেওয়া মোড়া, বাঁদিকে শতরঞ্জির ওপর ডেস্ক নিয়ে বসে আছেন মুনশীবাবুরা। ফৌজদার গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, "নাম কী?""শোভারাম দে।""কতদূর পড়েছ?""সংস্কৃত, আরবী-ফার্সি পড়েছি।""কোথায়?""টোলে, মক্তবেও।"
উত্তর শুনে ফৌজদার সন্তুষ্ট হলেন। মেহেদি রাঙানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "পড়তেই হবে, কায়স্থের ছেলে! শাস্ত্রও জানতে হবে, হিসাবও। তোমার বাবা ছিলেন এ অঞ্চলের বিখ্যাত পণ্ডিত, দেওয়ান মুর্শীদকুলি খাঁও তাঁকে প্রায়ই ডাকতেন।"
কিন্তু শোভারামের স্মৃতিতে বাবার উপস্থিতি আবছা। মাত্র চার বছর বয়সে হারিয়েছে তাঁকে। অনেকক্ষণ চেষ্টায় মনে পড়ে ফর্সা, লম্বা, গম্ভীর মুখের এক পুরুষ, মাথায় রঙিন পাগড়ি, আঁটোসাটো ট্রাউজারের ওপর হাঁটু পর্যন্ত ঝুলানো লম্বা কোট, ঘোড়ায় চড়ে কাছারির পথে যাত্রা।
যাক, স্মৃতি থাক বা না থাক, প্রয়াত পিতার নামেই মাত্র সতেরো বছর বয়সে শোভারামের চাকরি হয়ে গেল পাণ্ডুয়ার ফৌজদারী সেরেস্তায়। সে সময় বাংলায় জমিজমার হিসাব রাখার জন্য আসলি জামা তুমার নামে এক নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। নাকসীমহল্লার মুনশী সাদাতুল্লা এই ব্যবস্থার প্রধান কর্ণধার, তাঁর অধীনেই শোভারামের কর্মজীবনের সূচনা।
একদিকে ইলছোবা-মণ্ডলাই গ্রামের পুকুর-বাগান ঘেরা পৈতৃক বাড়ি, বিধবা মা, আর অন্যদিকে সদ্য পাওয়া চাকরি—নতুন জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। তখন বাংলায় আলিবর্দী খাঁর আমল, দোর্দণ্ডপ্রতাপে শাসন চালাচ্ছেন তিনি। তাঁর পূর্বসূরি মুর্শীদকুলি খাঁই প্রথম জমিদারদের ওপর অতিরিক্ত কর—আবওয়াব—আরোপ করেছিলেন, যা আলিবর্দীর সময়ে দশগুণ বৃদ্ধি পায়।
এই বিপুল রাজস্বের হিসাব রাখতে দক্ষ কর্মীর অভাব ছিল। বেশির ভাগ হিসাবরক্ষক গরমিল করত, বিশ্বস্ত লোক পাওয়াও দুষ্কর ছিল। কেউ কেউ সুযোগ বুঝে অর্থ আত্মসাৎ করত। কিন্তু শোভারাম দ্রুতই নিজের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন। ফৌজদার তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে পদোন্নতি দেন এবং মজুমদার পদবি প্রদান করেন। সেদিন থেকেই শোভারাম দে পরিচিত হলেন শোভারাম দে মজুমদারনামে।
জীবনের ধারা প্রবাহিত হলো—উত্তরাধিকার সূত্রে মান-সম্মান, বিত্ত, বৈভব সবই পেয়েছিলেন শোভারাম। এবার নিজের যোগ্যতায় ধাপে ধাপে তা আরও বাড়িয়ে তুললেন। যথাসময়ে বিয়ে, তিরিশ বছর বয়সে প্রথম সন্তানের জন্ম—সেই শিশুর হাসি-কান্নায় বহুদিন পর প্রাণ ফিরে এল পরিবারে। শোভারামের মা অপরূপ সুন্দরী কন্যার নাম রাখলেন স্বর্ণপ্রভা।
সন্তানের সান্নিধ্যে দিন কাটছিল আনন্দে, তবু মনের কোণে এক শূন্যতা দানা বাঁধছিল—একটি পুত্রের অভাব। এত বিশাল সম্পত্তি, ব্যবসা দেখবে কে? কন্যা তো চিরকাল বাবার ঘরে থাকবে না!
১৭৭০ সাল। ভয়াল এক বছর—সময়টি বাংলা ১১৭৬ সাল হওয়ায় এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ নামে পরিচিত। বাংলায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ, একবাটি ফেনের জন্য লড়াইয়ে মরছে মানুষ। কিন্তু শোভারামের ঘরে অন্নাভাব ছিল না, অভাব ছিল শুধু এক পুত্রের।
কিন্তু বিধাতা যেন তাঁকে বিস্মৃত হননি। শোনা যায়, কুলদেবী বিশ্বেশ্বরী স্বপ্নে এসে আশীর্বাদ করেন শোভারামের স্ত্রীকে। এবং সত্যিই, সে বছরই তিনি পুত্রসন্তানের মুখ দেখলেন। দেবীর কৃপায় পাওয়া এই সন্তানকে তিনি নাম দিলেন উমাপ্রসাদ।
স্বর্ণপ্রভা ধীরে ধীরে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠল, আর সময়ের রীতি মেনে মাত্র ন'বছর বয়সে শোভারাম তার বিয়ে দিলেন এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে। ধুমধামে অনুষ্ঠিত হল সেই বিবাহ—সাধারণ নিমন্ত্রণ নয়, দশ গাঁয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানানো হল সংবাদ। চার দিনের উৎসব—প্রথম দু’দিন সেরেস্তাদারদের আপ্যায়ন, পরের দু’দিন হিন্দু-মুসলমানদের জন্য পৃথক ভোজের আয়োজন। এত আড়ম্বরে আয়োজিত এই বিবাহ বহুদিন ধরে এলাকায় গল্প হয়ে রইল।
কিন্তু জীবনের চাকা ওঠে আর নামে—শোভারামের ভাগ্যও সেভাবেই ঘুরল। মাত্র দুই বছর পার হল, স্বর্ণপ্রভার তখনও দ্বিতীয়বার বাপের বাড়ি ফেরা হয়নি, এমন সময় খবর এলো—দু’দিনের জ্বরে জামাতা মারা গেছেন।
এই আঘাতে একেবারে ভেঙে পড়লেন শোভারাম। সিরাজের পতন, হেস্টিংসের অরাজকতা—এত কিছু সামলেছেন, কিন্তু কন্যার অকালবৈধব্য তাঁকে দিশাহারা করে দিল।
তবে সময়ই বড় চিকিৎসক—ধীরে ধীরে শোককে আটকে রাখলেন মনের গহীনে, কাজে নিজেকে আরও বেশি ডুবিয়ে দিলেন। ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়লেন, হেস্টিংসের পাঁচসালার বিশৃঙ্খলা পেরিয়ে দশসালার যাবতীয় সংকট সামলালেন। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধেও তাঁকে লড়তে হলো—১৭৮৪ সালের বিধ্বংসী বন্যা, তার পরের দু’বছরের দুর্ভিক্ষ, আর শেষ পরিণতি ১৭৮৭-র ভয়াবহ ঝড়ে।
দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আহার-নিদ্রা ভুলে তিনি কাজ করে গেলেন। আর এই সংকটময় সময়েই রাজা-প্রজা উভয়ের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন ছত্রধারী, ত্রাতা!
শাস্ত্র বলে, কর্মে অধিকার, ফলে নয়। শোভারামের জীবনে এ কথাই প্রতিটি পদক্ষেপে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। জীবনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করেও তিনি আশানুরূপ প্রতিদান পাননি। বরং বিপদ এল সেখান থেকেই, যার জন্য এত পরিশ্রম করেছিলেন—ফৌজদারের দিক থেকে।
ফৌজদারের এক শ্যালক ছিল, নারী, অর্থ, ও সুরায় আসক্ত। মাঝে মাঝেই ভগ্নীপতির জমিদারিতে এসে অরাজকতা সৃষ্টি করত। ফৌজদার ছিলেন নীতিনিষ্ঠ, তবে স্নেহ অতি বিষম বস্তু—অপুত্রক বৃদ্ধ শ্যালকের দোষের প্রতি চোখ বুজে থাকতেন।
শোভারাম আগেও বহুবার শক্ত হাতে এই শ্যালকের অনাচার ঠেকিয়েছিলেন, কিন্তু এ যেন এক অন্তহীন যুদ্ধ।
একদিন শোভারাম সেরেস্তা থেকে ফিরে মধ্যাহ্নভোজনে বসেছেন, কিন্তু দেখতে পেলেন স্বর্ণপ্রভা নেই। দীর্ঘদিনের অভ্যাস—মেয়ে সামনে না থাকলে তাঁর আহার তৃপ্ত হয় না। ইতস্তত করে গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করলেন, “স্বর্ণ কোথায়?” ঘোমটার আড়াল থেকে স্ত্রী দায়সারা উত্তর দিলেন।
খাওয়া শেষ হয়ে এল, তবু কন্যার দেখা নেই। অবশেষে শোভারাম নিজেই তার খোঁজ করলেন। এবার গৃহিণী চাপাস্বরে কাঁদতে থাকেন। কিছু না বুঝে শোভারাম সরাসরি স্বর্ণর ঘরে গেলেন। দেখেন, খাটের উপর সে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তুলতেই সে অঝোরে কাঁদতে থাকে।
নিষ্পাপ বালবিধবা ভয়ে-লজ্জায় বাবার সামনে কিছুই বলতে পারে না। অবশেষে জানা গেল, দীঘিতে স্নান সেরে ফেরার সময় স্বর্ণপ্রভার সামনে পড়ে যায় ফৌজদারের শ্যালক। ঘোড়া থেকে নেমে সে পথ আটকে দাঁড়ায়... বাকিটা আর বলতে পারে না মেয়ে। শুধু কান্নায় ভেঙে পড়ে!
প্রাণাধিক কন্যার অপমানে শোভারাম ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। তৎক্ষণাৎ ফৌজদারের কাছে গিয়ে শ্যালককে শাস্তি দিতে মনস্থির করেন। কিন্তু ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হতেই মনে প্রশ্ন জাগে—তাতে কী হবে?
ফৌজদারের দুর্বলতা তো অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে! হয়তো একটু বকাঝকা করবেন, কিন্তু তাতে কিছুই বদলাবে না। বরং এই নির্লজ্জ শয়তান আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে! নিজের কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে শোভারাম আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।
শোভারামের মাথা ঘুরতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন, পুকুরঘাটের ঘটনা গোপন থাকবে না। গ্রামের মেয়েরা রসিয়ে পাঁচকান করবেই। ব্রাহ্মণ সমাজ সন্ধ্যার সভায় বিধান দেব—পতিত কন্যাকে বাড়ি ছাড়া করো!
আর স্বজাতি কায়স্থেরা, যারা দীর্ঘদিন ধরে শোভারামের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলেছে, তারাও নিশ্চয়ই এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না।
অস্থির হয়ে পড়েন শোভারাম। কখনো বসেন, কখনো উঠে দাঁড়ান, কখনো পায়চারি করেন, কখনো ঘরের দরজা বন্ধ করে নির্জনে বসে থাকেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়, রাস্তা ফাঁকা হতে থাকে।
হঠাৎ সর্বাঙ্গে চাদর মুড়িয়ে চুপিসারে বাড়ির বাইরে যান তিনি। অল্প কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে শলা-পরামর্শ করেন। তারপর ঝড়ের গতিতে শুরু হয় প্রস্তুতি!
তিন ঘণ্টার মধ্যে মূল্যবান সব অস্থাবর সম্পত্তি বাক্সবন্দি হয়। বাড়ির একজন বিশ্বস্ত চাকর ছাড়া কেউ কিছুই বুঝতে পারে না!
মাঘ মাসের হাড়কাঁপানো শীত। মধ্যরাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে তিনখানা পালকি এসে থামল বাড়ির দরজায়। স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে পালকিতে উঠলেন শোভারাম। প্রথম পালকিতে উমাপ্রসাদ, দ্বিতীয়টিতে স্ত্রী, আর তৃতীয়টিতে স্বর্ণপ্রভাকে নিয়ে তিনি নিজে। সঙ্গে যা সম্ভব, টাকা-পয়সা, সোনাদানা ভাগ করে নিলেন।
সে সময় এলাকায় ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন হয়নি, অভিজাতদের বাহন ছিল হাতি, ঘোড়া, পালকি। শোভারামের বাড়িতে পালকির যাতায়াত নিত্যদিনের ব্যাপার, তাই কারও সন্দেহ হওয়ার সুযোগ ছিল না—কাকপক্ষীও টের পেল না।
ভয়, শঙ্কা, অপমান, বেদনার ভারে প্রায় দুইশো বছরের পৈতৃক ভিটে, কুলদেবী, জমি-সম্পত্তি সব ছেড়ে অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের পথে যাত্রা করলেন শোভারাম। তখন তিনি জীবনের শেষ অধ্যায়ে—বয়স পঞ্চান্ন ছুঁইছুঁই। স্বর্ণপ্রভার বয়স পঁচিশ, উমাপ্রসাদ সদ্য যৌবনোত্তীর্ণ, কুড়ির কাছাকাছি।
প্রথম গন্তব্য ছিল তারকেশ্বর। ইলছোবা থেকে তারকেশ্বরের পথ সহজ ছিল না। আজকের বাসে পাণ্ডুয়া থেকে তারকেশ্বর সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ, কিন্তু সে সময়ের দুর্বল রাস্তায় সেই যাত্রা ছিল আরও কঠিন, আরও অনিশ্চিত।
সে কালে জি টি রোড পেরিয়ে নিশ্চয়ই কোনও হাঁটাপথ ছিল, হাজারো তীর্থযাত্রী সেই পথেই শিবদর্শনে যেতেন। কিন্তু শোভারামের সমস্যা ছিল অন্যত্র—তিনি ছিলেন সুপরিচিত, শুধু কাছাকাছি নয়, দূরদূরান্তেও। তাই গোপনে পালিয়ে আসতে গিয়ে সোজা পথে আসা সম্ভব হয়নি।
পাঁচ মাইল জুড়ে প্রাচীরবেষ্টিত পাণ্ডুয়া নগরের বাইরের পথ ধরে, যতটা সম্ভব অচেনা ও নির্জন পথ বেছে নিলেন তাঁরা। অবশেষে তারকেশ্বরে পৌঁছে একদিন বিশ্রাম নিলেন, কারণ সেখানে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিলেন।
এরপর গোযানে প্রবল পথক্লেশ ও বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তাঁরা পৌঁছান হাওড়ার পাতিহালে। কী সূত্রে সেখানে এলেন, তা স্পষ্ট নয়, তবে অনুমান করা যায়—তৎকালীন পাতিহালের জমিদার রায়বাবুদের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল, সেই কারণেই নিরাপদ আশ্রয় ভেবে তাঁরা সেখানে আশ্রয় নিলেন।
শোভারাম তেমন কিছু আনতে পারেননি, যা সামান্য এনেছিলেন, তা দিয়েই পাতিহালে নতুন জীবন শুরু করলেন। পুত্র উমাপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হলো।
কঠোর পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা, ও বুদ্ধি—এই তিন মূলধনকে সম্বল করে ধীরে ধীরে জমি বাড়াতে থাকলেন তাঁরা। ইতিমধ্যে উমাপ্রসাদের বিয়ে হলো এবং বহু প্রতীক্ষার পর তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মাল—যার নাম শোভারাম নিজেই রাখলেন বরদাপ্রসাদ।
শেষ জীবনে ইলছোবা ছাড়ার দুঃখ অনেকটাই কাটিয়ে উঠলেন শোভারাম। উদ্বাস্তু হলেও জীবদ্দশাতেই উমাপ্রসাদকে গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠিত রায়ত হিসাবে দেখতে পেলেন। এবং বেশ সমর্থ থাকতেই, জীবনযুদ্ধের এই সংগ্রামী সৈনিক ছিয়াশি বছর বয়সে দেহত্যাগ করলেন।