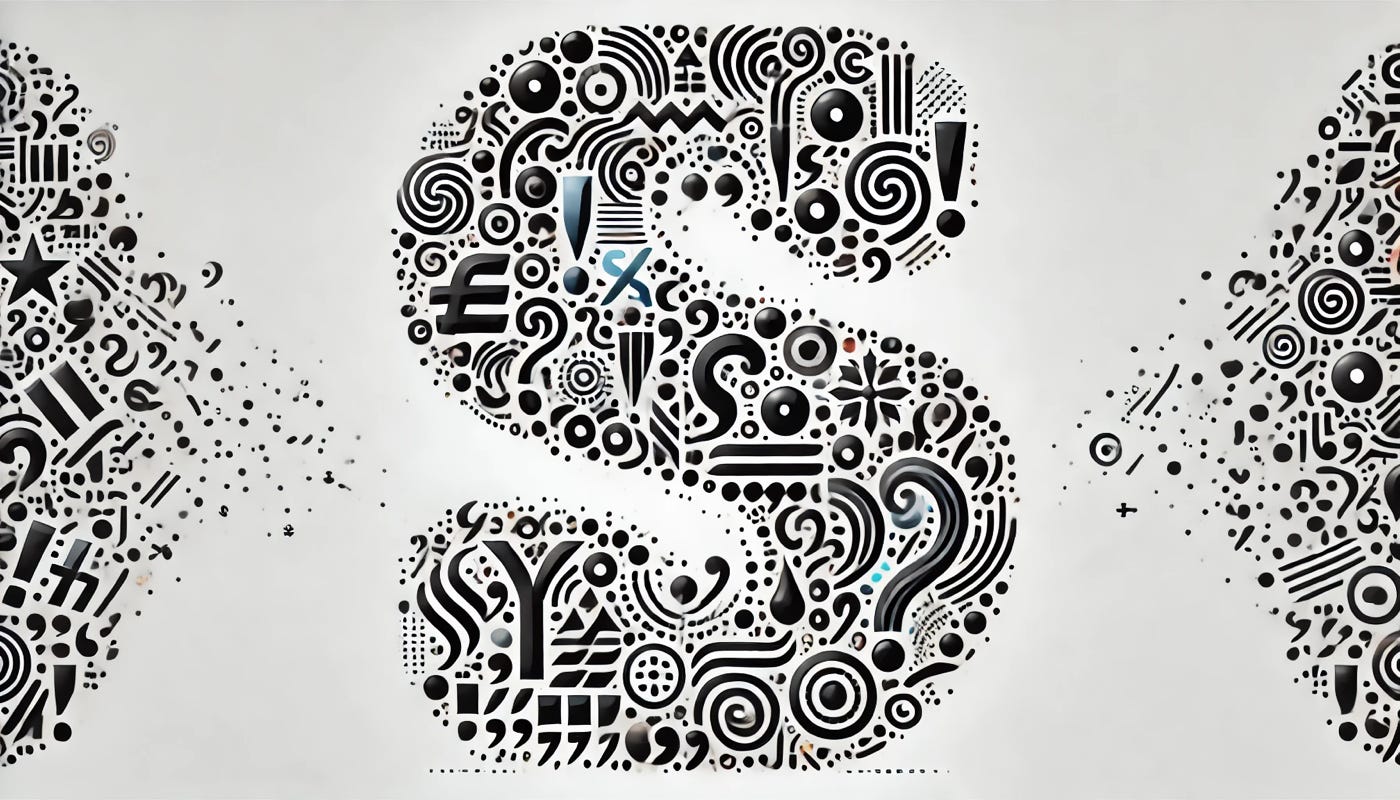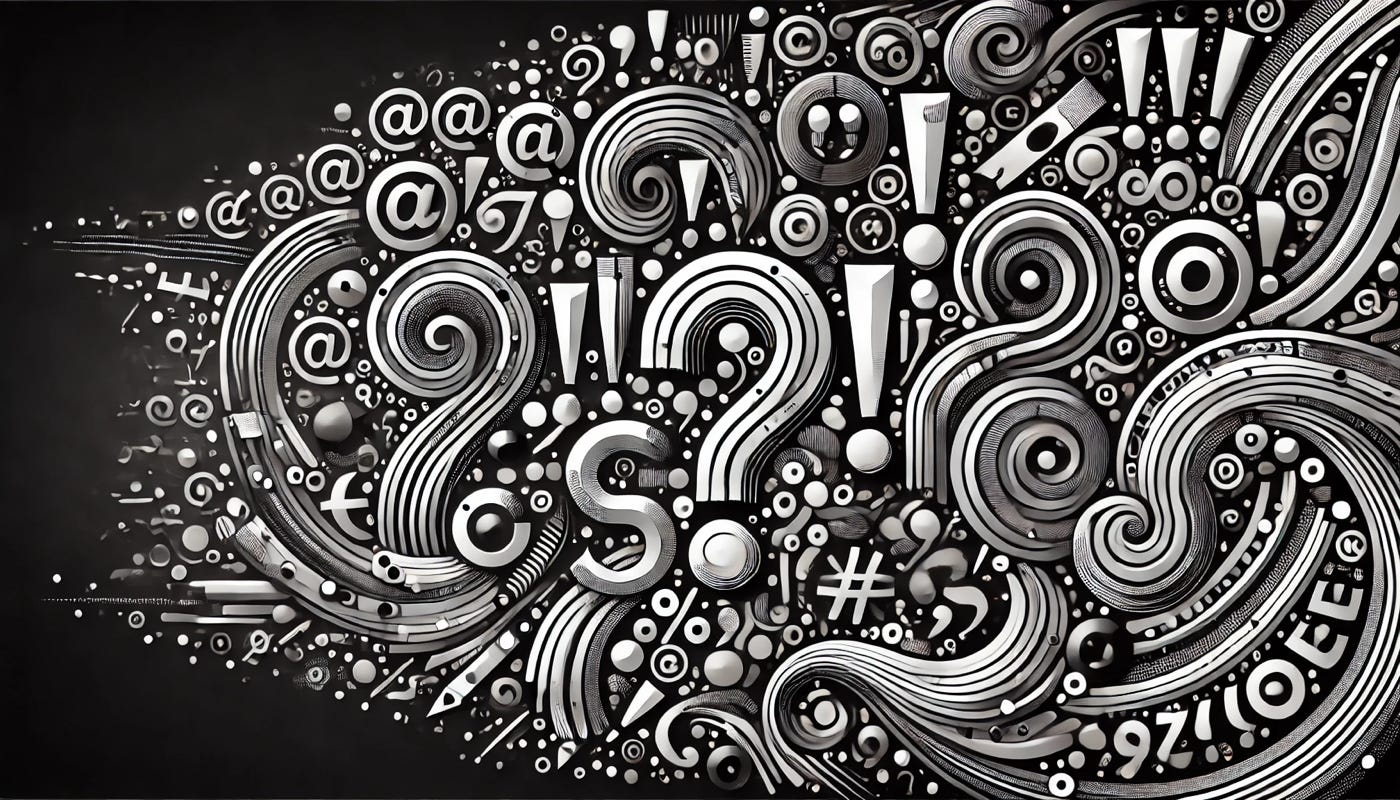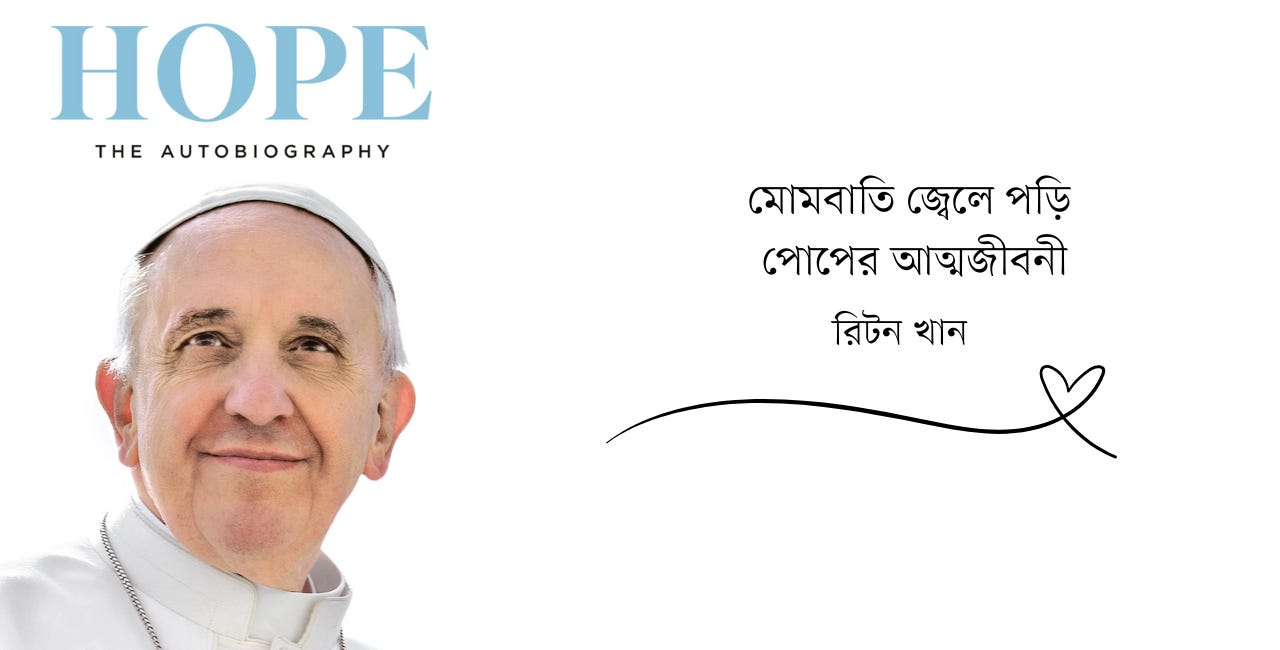যতিচিহ্ন ইতিহাস ও বিবর্তন
‘যতিচিহ্ন’, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Punctuation, আজকের পৃথিবীতে সবার পরিচিত। এর আবিষ্কার কবে, কখন, বা কোথায় হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে ধারণা করা যায়, আদি মানুষ নিজের পড়ার প্রয়োজনে যতিচিহ্ন’ সৃষ্টি করে
যদিসমস্তলেখাএমনগুঁজেগুঁজেলেখাহতোতাপড়াপ্রায়অসম্ভবহয়েযেতএকেকটিশব্দকোথায়শেষহয়আরপরেরটিকোথায়শুরুহয়তাবুঝতেবিরাটকষ্টহত। ভয় নেই, এমন লেখা আর পড়তে হবে না। এটি কেবল একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ যে, লেখার আশেপাশের ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কত মূল্যবান—যেগুলো শব্দ নয়, অথচ শব্দকে বোঝার জন্য অত্যন্ত জরুরি। যেমন, শব্দের মধ্যবর্তী ফাঁক (space), যা পড়ার আনন্দ এবং বোধগম্যের জন্য বড় ভূমিকা রাখে। শত শত বছর ধরে, সমস্ত লেখা এমন গুঁজে লেখা হতো—বড় হাতের অক্ষর বা শব্দের মধ্যে ফাঁক ছাড়াই।
‘যতিচিহ্ন’, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Punctuation, আজকের পৃথিবীতে সবার পরিচিত। এর আবিষ্কার কবে, কখন, বা কোথায় হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে ধারণা করা যায়, আদি মানুষ নিজের পড়ার প্রয়োজন এবং জীবনের চাহিদা থেকে ধীরে ধীরে ‘যতিচিহ্ন’-এর সৃষ্টি করেছে।
আসলে, তখন কমা, অ্যাপস্ট্রফি, ড্যাশ, প্রশ্নবোধক চিহ্ন তো ছিলই না, এমনকি সেমিকোলনেরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না (যা ব্যবহার করার নিয়ম এখনো অনেকেই জানে না)। এমনকি বাক্য শেষ করার জন্য কোনো দাড়ি (.) ছিল না। আজকের দিনে যতটা স্বাভাবিক মনে হয় যতিচিহ্ন, ততটাই কষ্টসাধ্য ছিল এর আবিষ্কার। এটি কোনো প্রতিভাধর লেখক বা মুদ্রাকরের মাথা থেকে হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়নি; বরং এটি ধীরে ধীরে, পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। এর প্রসার ও পুনরুজ্জীবন নির্ভর করেছে ব্যক্তিগত চিন্তাবিদ, প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপট এবং পাঠকসমাজের ওপর। এটাই যতিচিহ্নের গল্প।
এই সবকিছুর শুরু একজন গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে, যিনি পাঠকদের জন্য পড়া সহজ করতে চেয়েছিলেন। প্রায় দুই হাজার বছর আগে, গ্রিক প্রভাবিত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল গ্রন্থাগারে প্রাচীনকালের সেরা অসংখ্য পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু তখন লেখা শুধুমাত্র কথার রেকর্ড হিসেবে বিবেচিত হতো (ভাষার নিজস্ব নিয়ম বা আচরণের স্বতন্ত্র প্রকাশ নয়), তাই পাঠ একটানা অক্ষর দিয়ে লেখা হতো, কারণ কথার মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না। সে সময় মানুষ ভাবেনি শব্দগুলোকে আলাদা করার প্রয়োজন। লেখাকে অধ্যয়নের জন্য তৈরি করা হতো, এবং এটি পড়া হতো উচ্চস্বরে। চট করে একটি শব্দ পড়ার ধারণাই তখন ছিল না!
এই পরিস্থিতি পড়া ও বোঝার কাজকে কঠিন করে তুলেছিল; পাঠকদের পাঠ্যের মর্মোদ্ধার করতে অবশ্যই ব্যাকরণ ভালোভাবে জানতে হতো। আরিস্টোফেনেস, ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান গ্রন্থাগারিক লক্ষ্য করলেন, গ্রীক ভাষায় দক্ষ নয় এমন পাঠকরা তার গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি পড়তে বেশি সময় নিচ্ছেন, যা ভাষায় দক্ষদের তুলনায় অনেক বেশি। এই সমস্যা সমাধানে তিনি একটি প্রাথমিক যতিচিহ্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন—যেখানে ফাঁক ছিল না, তবে লাইনের বিভিন্ন স্তরে অক্ষরের মধ্যে ছোট্ট বিন্দু বসানো হতো। এটি বাক্য শেষ এবং বাক্যের মধ্যে বিরতির জন্য ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে এগুলোই আমাদের বর্তমান দাড়ি, কোলন ও কমায় রূপান্তরিত হয়।
সবাই কিন্তু এই ধারণাকে স্বাগত জানায়নি; কিছু প্রাচীন লেখক, যেমন রোমান চিন্তাবিদ সিসেরো, এ নিয়ে ব্যঙ্গও করেছিলেন। তিনি তুচ্ছজ্ঞান করতেন নবীন পাঠকদের, যারা লেখার মধ্যে বিন্দুর সাহায্য ছাড়া পড়তে পারতেন না। যারা নিজেরাই বাক্যের গঠন বুঝতে পারতেন না, তার ছন্দের উত্থান-পতন এবং বিভিন্ন ব্যাকরণিক অংশের প্রাকৃতিক বিরতিগুলো অনুভব করতে পারতেন না। সিসেরোর মতে, যারা যতিচিহ্ন ছাড়া পড়তে পারে না, তাদের হয়তো আদৌ পড়া উচিত নয়!
তবুও প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে এমনকি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিরাও প্রাচীন লেখার ধারাবাহিক অক্ষরগুলো পড়ার জন্য যতিচিহ্নের উপর নির্ভর করতেন। রোমান যুগের লেখাগুলোতে দেখা যায় ব্যতিক্রমধর্মী চিহ্ন, যা পাঠকদের কোথাও বিরতি নিতে বা কোনো শব্দে জোর দিতে সাহায্য করত। এইসব চিহ্নিত সংস্করণকে বলা হতো “কোডিসেস ডিস্টিন্টি,” অর্থাৎ “প্রভেদযুক্ত বই”—যেখানে অক্ষর বা ব্যাকরণিক এককগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে বিন্দু ব্যবহার করা হতো। সময়ের সাথে সাথে, যখন রোমান সাম্রাজ্য নানা জাতি, অর্থনৈতিক সংকট ও সামরিক চাপের কারণে ভেঙে পড়তে শুরু করে, তখন দক্ষ পাঠক খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং মানুষের পাঠ দক্ষতাও ক্ষীণ হতে থাকে। এই “কোডিসেস ডিস্টিন্টি” তখন মূল্যবান বস্তু হয়ে ওঠে, এবং প্রাচীন জ্ঞানকে পুনরুদ্ধারের জন্য এক অপরিহার্য উপায় হয়ে দাঁড়ায়।
একই সময়ে, খ্রিস্টান চার্চ রোমানদের পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক শক্তিকে প্রতিস্থাপন করে আত্মিক শাসনের মাধ্যমে জনগণের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরা শব্দগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। কারণ যারা ঈশ্বরের বাণীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, তারাই মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর যেহেতু যতিচিহ্ন লেখার অর্থ উন্মোচন করে, এটি সাধারণ মানুষের হাতের বাইরে রাখাই ছিল তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া, যারা প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইবেল পড়তেন, তারা এতটাই পরিচিত ছিলেন এর শব্দগুলোর সাথে যে, তাদের কোনো নির্দেশনার প্রয়োজনই পড়ত না।
বিশপ বা পোপের বন্দিশালা থেকে এই ছোট্ট বিন্দুগুলো ধীরে ধীরে উত্তর দিকে ছড়িয়ে পড়ে, পরিচিত জগতের বাইরে পৌঁছে যায় এবং পড়া ও লেখার রূপকে পরিবর্তিত করে দেয়। শব্দের মাঝে ফাঁক থাকা পাঠ্যরূপে এটি আমাদের পরিচিত লেখার আধুনিক কাঠামো গড়ে তোলে।
নবম শতকের কোনো এক সময়—ঠিক কখন বা কার মস্তিষ্কপ্রসূত, তা আমরা জানি না—দূরবর্তী আয়ারল্যান্ডের সন্ন্যাসীরা ল্যাটিন শব্দগুলোর মাঝে ছোট ছোট ফাঁক যোগ করতে শুরু করেন। তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল গেইলিক, যা ল্যাটিনের থেকে ভিন্ন; ফলে শব্দের শুরু ও শেষ চিহ্নিত করতে তাদের সমস্যায় পড়তে হতো, যা বিদেশি ভাষা শেখাকে কঠিন করে তুলত। আজকের কোটি কোটি পাঠক সেই আয়ারল্যান্ডের সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা ল্যাটিন ভালোভাবে না জানার কারণে এই ব্যবস্থাটি উদ্ভাবন করেছিলেন।
মধ্যযুগে লেখার ধারণায় পরিবর্তন আসে; এটি ভাষার একটি স্বতন্ত্র রূপে পরিণত হয়। ইতিহাসে প্রথমবার, লেখা শুধু উচ্চস্বরে পাঠ করার জন্য সীমাবদ্ধ থাকল না; বরং এটি নিঃশব্দে পড়া বা একাকী পাঠকের নিজের মনে ফিসফিস করে উচ্চারণ করার মাধ্যমেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। ফলে, উচ্চারণ ছাড়াই লেখার সুর বা টোন বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন যতিচিহ্ন এই শূন্যতা পূরণ করে এবং সাধারণ ব্যাকরণিক নির্দেশনার চেয়ে লেখার আবেগ ও পরিবেশনাভঙ্গি নির্দেশ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে।
মধ্যযুগের পরবর্তী সময়ে প্রশ্নবোধক চিহ্নের আবির্ভাব ঘটে। এর প্রথম দিকের আকার ছিল অনুভূমিক, যা দেখে মনে হতো এটি ডানদিকে লাইনের কোণে টেনে নেওয়া হচ্ছে (এভাবে .~)। ধীরে ধীরে এটি সোজা হয়ে বর্তমানের পরিচিত চিহ্নে পরিণত হয়। এর আকারের উৎস নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। কেউ মনে করেন, এটি মধ্যযুগের গির্জার সঙ্গীতের স্বরোন্নতির চিহ্ন থেকে ধার করা হয়েছে, যা কণ্ঠস্বর উঁচু করার নির্দেশ দিত। আবার অন্যরা বলেন, এটি ল্যাটিন শব্দ quaestio (প্রশ্ন) থেকে এসেছে, যেখানে ‘q’ এবং ‘o’ একত্রে ব্যবহার করা হতো। প্রায়ই এটি পাঠকের সুবিধার্থে লাইনের শেষে বা মার্জিনে প্রশ্নবোধক অর্থে উল্লেখ করা হতো।
শব্দের মধ্যে ফাঁক, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, কমা, দাড়ি (.)—১৪০০ সালের মধ্যে যতিচিহ্নের বিকাশ মিশরের আরিস্টোফেনেসের কল্পনারও বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তনের এখানেই শেষ নয়।
চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে, ইতালি থেকে শুরু হয়ে পুরো ইউরোপে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে একটি প্রবণতা গড়ে ওঠে যা ছিল আকর্ষণীয় ও শৈলিবদ্ধ লেখার প্রতি গভীর আগ্রহ। পণ্ডিতেরা দুর্গম পর্বতমালার আড়ালে লুকানো প্রাচীন গ্রন্থাগারে খুঁজে বেড়াতেন পাণ্ডুলিপি, যেখানে তাদের প্রিয় লেখক হোমার, ভার্জিল, সিজার বা ক্যাটুলাসের মূল ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার কাছাকাছি লেখা পাওয়া যায়। তারা মধ্যযুগীয় ল্যাটিনকে বিকৃত ও কুৎসিত বলে মনে করতেন, যা শত শত বছরের অবক্ষয়ের ফলে গড়ে উঠেছিল। আমরা তাদের আজ হিউম্যানিস্ট বলি, লক্ষ্য ছিল প্রাচীনদের ভাষা ও গুণাবলিকে অনুকরণ করা। গল্প ও শৈলীর মাধ্যমে অতীতের প্রতি যে নতুন রকমের সংযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে লিখিত শব্দ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই এক অভূতপূর্ব মর্যাদা লাভ করে।
লেখা তখন শুধু তথ্যের বাহক ছিল না; এটি আরও সূক্ষ্ম বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্বও পালন করত। এর মাধ্যমে বিষয়বস্তু সরল ও শৈল্পিকভাবে প্রকাশ করতে হতো; নির্দিষ্ট সুর বা আবেগ বোঝাতে হতো; এমনকি কখনো পাঠের ধরণও নির্দেশ করতে হতো। হিউম্যানিস্টরা, আজকের আমাদের মতোই, লেখার অস্পষ্টতা বোঝার চেষ্টা করতেন। বর্তমানে যখন ফোনের কোনো মেসেজ “Read” হিসেবে চিহ্নিত হয়, তত্ক্ষণাত আমরা কোন ভুল সংশোধন করার জন্যে তড়িঘড়ি করে হাসির ইমোজি পাঠাই। যদিও ইমোজি ছবি, আর কমা বা কোলনের মতো স্বেচ্ছাচারী চিহ্ন নয়, তবু এদের ভূমিকা এক। এগুলো ভাষাকে এমন অংশে বিভক্ত করে, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য, অর্থবোধক এবং বুঝে নিতে সাহায্য।
পুনর্জাগরণের যুগের ইমোজির সঙ্গে তুলনীয় ছিল বিস্ময়বোধক চিহ্ন, যা চতুর্দশ শতকের শেষদিকে হিউম্যানিস্ট ইয়াকোপো আলপোলেইও প্রস্তাব করেন “admirative” বাক্যাংশ—অর্থাৎ বিস্ময়ের অভিব্যক্তি চিহ্নিত করার জন্য। যেমন, বিস্ময়! এর ঠিক পরে আসে বন্ধনী, যা ১৩৯৯ সালে আইনজীবী ও পণ্ডিত কোলুচিও সালুতাতি প্রবর্তন করেন। এটি বাক্যের অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহকারী অংশগুলোকে আলাদা করতে ব্যবহৃত হতো, যেগুলো মূল অর্থের জন্য অপরিহার্য নয়। ১৪৯৬ সালে ভেনিসের মুদ্রক আলদো মানুজিও অ্যাপস্ট্রফ এবং দুর্ভেদ্য সেমিকোলন যুক্ত করেন। অ্যাপস্ট্রফ নির্দেশ করে যে কোনো অক্ষর বাদ পড়েছে (যেমন “it’s” মানে “it is”), আর সেমিকোলন একটি সূক্ষ্ম বিরতি নির্দেশ করে—কমা ও কোলনের মাঝামাঝি কিছু; একপ্রকার ভাবের বিরতি, দম নেওয়ার সুযোগ।
শেক্সপিয়ারের লেখায়, আজ আমরা যেসব যতিচিহ্ন ব্যবহার করি তার প্রায় সবই আবির্ভূত হয়। তবে কোটেশন মার্ক, ড্যাশ বা ইলিপসের (…) মতো চিহ্ন তখনো লেখক ও পাঠকদের বিভ্রান্ত করত এবং এগুলোর ব্যবহার গড়ে উঠতে আরও এক শতাব্দী সময় লেগেছিল। যতিচিহ্নের গল্প এভাবে বললে তা সোজাসাপ্টা মনে হতে পারে, কিন্তু এটি এখনো ভুলে ভরা অন্ধগলিতে নিয়মের মায়াজালে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে।
সত্যি বলতে, যতিচিহ্নের নিয়ম রয়েছে, আবার নেইও। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা আমরা সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলেছি, তাই চাইলেই এটি বদলে দিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, উনিশ শতকে যতিচিহ্নের ছড়াছড়ি দেখা যায়, যখন অপ্রয়োজনীয় চিহ্নে পৃষ্ঠাগুলো ভরে উঠত, যেন পিঁপড়ের সারি। এর মধ্যে “কমাশ” বা “কমা ড্যাশ” (, -) ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগের বিখ্যাত উদ্ভাবন। তখনকার ধারণা ছিল, “যত বেশি, তত ভালো”। তবে এই যতিচিহ্নের বন্যা কুড়ি শতকে উল্টো পথে মোড় নেয়, যখন লেখকরা—আর্নেস্ট হেমিংওয়ে—কম যতিচিহ্ন ব্যবহার করা অনুসরণের চেষ্টা করেন।
ডিজিটাল যুগে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যতিচিহ্নও বদলে গেছে। একসময় যে দাড়ি (.) নিরপেক্ষতার প্রতীক ছিল—“এখানে বাক্য শেষ হলো”—এখন তা দমন করা আবেগ প্রকাশের বাহক হয়ে উঠেছে। আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল যোগাযোগে যতিচিহ্নের ব্যবহার নিয়ে কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়েছি। যখন হাইফেনের ঠিকঠাক ব্যবহারের চেয়ে দ্রুত টেক্সট করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তখন কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামায়? বর্তমান যুগের টেক্সট লেখাকে যতিচিহ্নের ধ্বংস বলা সহজ, কিন্তু তা আসলে নয়। বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো যতিচিহ্নের ধারণা প্রসারিত করছি, যেখানে পুরনো চিহ্নগুলোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন চিহ্ন, যেমন অ্যাস্টারিস্ক (*), হ্যাশট্যাগ (#), অ্যাম্পারস্যান্ড (&), আর অবশ্যই ইমোজি। এ ছাড়া, আমরা এখনো পরিস্থিতি আর মাধ্যম বুঝে যতিচিহ্ন ব্যবহারে বেশ দক্ষ। আপনি তো আপনার বসকে পাঠানো ইমেইলে চুমুর ইমোজি দেবেন না, ঠিক যেমনটি আপনি আশা করবেন না যে ব্যাংকের চিঠিগুলো ফেসবুকের এক লাইনের পোস্টের মতো দাড়িবিহীন সাজানো থাকবে।
যতিচিহ্নের বিবর্তন হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে, এবং তা ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। তবে আমরা তাদের প্রতি ঋণী যারা আমাদের আগে পরিশ্রম করে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, যা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় পড়াকে—আনন্দদায়ক করেছে। তাই, কখনো কোনো ভুল কমা বা বিপথগামী অ্যাপস্ট্রফি দেখে থমকে গেলে, কিংবা ঠিক কতগুলো বিস্ময়বোধক চিহ্ন আপনার আবেগ প্রকাশের জন্য যথাযথ তা ভেবে বিভ্রান্ত হলে, আলেকজান্দ্রিয়া, আয়ারল্যান্ড ও ভেনিসের সেই প্রাথমিক যতিচিহ্ন আবিষ্কারকদের কথা একবার ভাবুন। তারা আমাদের শব্দের প্রবাহে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং পড়ার আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তুলেছেন।