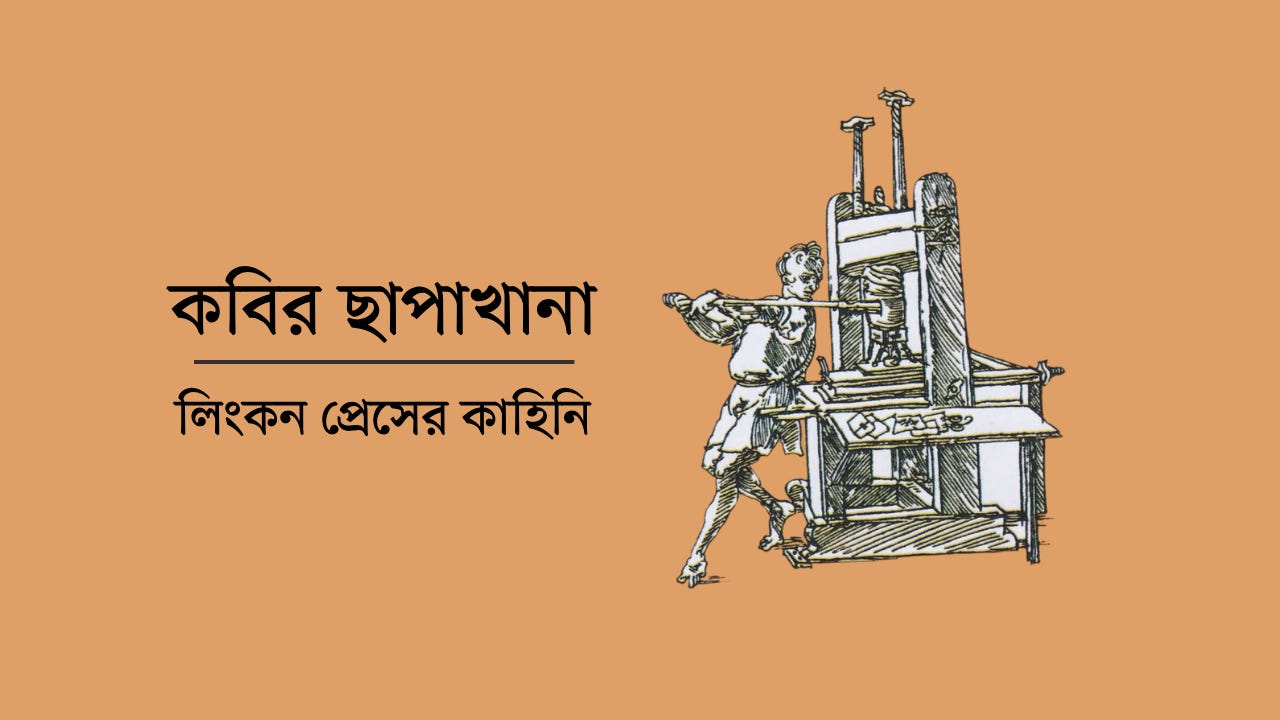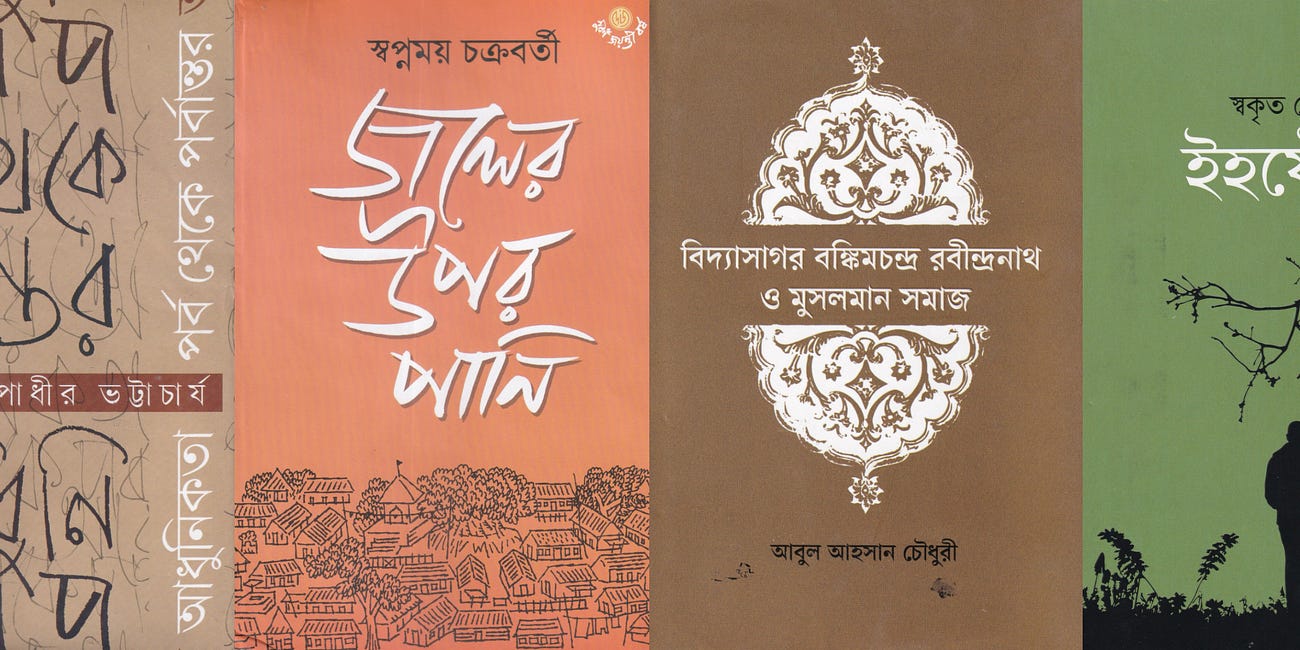রবীন্দ্রনাথের কোণার্ক ও লিংকন প্রেসের কাহিনি
রবীন্দ্রনাথের নির্জন নিবাস কোণার্ক ও লিংকন প্রেসের কাহিনি, লিংকন প্রেসের মাধ্যমে বিশ্বভারতীর সাহিত্যিক অভিযাত্রা।
১৯১৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সন ও মুকুল দে-কে সঙ্গে নিয়ে জাপান থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। জাহাজযাত্রার অভিজ্ঞতা মুকুল দে তাঁর আমার কথা বইতে চিত্রময়ভাবে তুলে ধরেছেন। তরুণ মুকুল কখনও মাস্তুলে জোড়া বাজপাখি দেখেন, কখনও দূরের বাঁকা দিগন্ত। ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁরা সিয়াটল বন্দরে পৌঁছান। কাস্টমসের সময় মুকুলের স্কেচ করা রবীন্দ্রনাথের কিছু চিত্র সাংবাদিকরা সংগ্রহ করে, যা ভোরে সিয়াটলের সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয়।
রবীন্দ্রনাথের এই সফরের আয়োজন করেছিলেন জুনিয়র জেমস বার্টন পন্ড। তাঁর বাবার মতোই তিনি বক্তৃতা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি আমেরিকায় চল্লিশটি বক্তৃতার চুক্তি করেন, প্রতি বক্তৃতার জন্য ধার্য হয় ৫০০ ডলার। এই অর্থ তখন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, কারণ তাঁর ৩০,০০০ টাকার দেনার সুদ ও অন্যান্য পরিকল্পনার জন্য অর্থ দরকার ছিল। বিদ্যালয়ের জন্য তহবিল, হাসপাতাল ও টেকনিকাল বিভাগ খোলার পরিকল্পনা, এবং পাকা বাড়ি নির্মাণ—সবই তাঁর উদ্দেশ্যের অংশ ছিল।
১৯ সেপ্টেম্বর লস এঞ্জেলস টাইমস-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমার এই বক্তৃতাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতের আমার বিদ্যালয়ের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।"
১৯১৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার বিষয় ছিল The Cult of Nationalism, যা নরমেধযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যুদ্ধের পদধ্বনি তখন স্পষ্ট, যদিও আমেরিকা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়নি। এর মাত্র মাস দেড়েক আগে, ৩০ জুলাই, নিউজার্সির ব্ল্যাক টম দ্বীপে অস্ত্রভাণ্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে এবং ২২ জুলাই সান ফ্রান্সিসকোতে যুদ্ধ প্রস্তুতির নামে মিছিল সংগঠিত হয়, যেখানে প্রাণহানিও ঘটে।
বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সীমান্তকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদকে আধুনিক যুগে কল্পিত রেখা হিসেবে চিহ্নিত করেন, তবে বোলপুর বিদ্যালয় তখনও তাঁর আলোচনায় আসে না। বিদ্যালয়টির স্বপ্ন তখনও তাঁর কল্পনার গভীরে প্রোথিত ছিল। ১১ অক্টোবর এক চিঠিতে তিনি লেখেন, শান্তিনিকেতন হবে ভারতের সঙ্গে বিশ্বের যোগসূত্র—একটি সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র, যা বিশ্বজাতির মহামিলনের প্রথম পদক্ষেপ হবে।
তবে, বাস্তবতা ছিল কল্পনার চেয়ে অনেক দূরে। শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করে এক সাহেব সান্তা বারবারায় একটি ইনস্টিটিউট তৈরি করেন। সেখানে আমন্ত্রণ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যা দেখেন, তা মুকুল দে তাঁর আমার কথা বইতে উল্লেখ করেন। সেই ইনস্টিটিউট তখনও অসম্পূর্ণ—দরজা-জানালা বসানো হয়নি, চারপাশে কাঠ, লোহা, পেরেক ছড়ানো। হাঁটার সময় রবীন্দ্রনাথের পায়ে পেরেক ফুটে রক্তক্ষরণ শুরু হয়, কিন্তু তিনি তা বুঝতেও পারেননি।
তৎকালীন আমেরিকাবাসীরা বোলপুর বিদ্যালয়কে সান্তা বারবারার নির্মীয়মাণ ইনস্টিটিউটের মতোই অপূর্ণ মনে করতেন, যা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নপূরণের পথে এক কঠিন বাস্তবতার ইঙ্গিত।
আমেরিকায় শান্তিনিকেতন ও বোলপুর বিদ্যালয়ের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য পিয়র্সন রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনে একটি বই লেখেন। বইটির নাম Santiniketan: The Bolpur School of Rabindranath Tagore, যা ম্যাকমিলান কোম্পানি ১৯১৬ সালের নভেম্বরে প্রকাশ করে। এতে ছিল আশ্রম-সংগীতের অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' গল্পের ইংরেজি অনুবাদ এবং মুকুল দে-র আঁকা ছবি। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় ভারতের তপোবনবাসী গুরুর শিক্ষা-আদর্শ তুলে ধরেন, যা সত্য, শান্তি ও মুক্তির সন্ধান দিত।
পিয়র্সন বোলপুরে প্রথম আগমনের স্মৃতি লিখেছেন বইটিতে। গোধূলিবেলার এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তাঁকে মনে করিয়ে দেয় বিদ্যালয়ের চেয়ে তীর্থের মতো অনুভূতি। ছাত্রদের সঙ্গে কথোপকথন, ছাদের ওপর চাঁদের আলোয় গান শোনা, সাঁওতাল গ্রাম এবং বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের জীবনচিত্র তাঁর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে।
বইয়ে পিয়র্সন শিশুদের সাহিত্য ও সৃজনশীলতার কথা বলেছেন। ছাত্রদের হাতে লেখা পত্রিকার বাৎসরিক উৎসব, গাছের পাতা ও পদ্মফুল দিয়ে সাজানো মঞ্চ এবং অভিনব সাহিত্যসভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সৃজনশীলতা শান্তিনিকেতনকে আত্মোপলব্ধি ও কল্পনার ভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
১৯১৭ সালের ৮ জানুয়ারি, নেব্রাসকার লিংকন শহরের অধিবাসীরা শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জন্য একটি ছাপার মেশিন উপহার দেন, যা স্কুলের সৃষ্টিশীলতাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার প্রয়াস হিসেবে দেখা যায়। পিয়র্সনের বই এবং এই উপহারের মধ্যে এক গভীর সাংস্কৃতিক যোগসূত্র প্রতিফলিত হয়। এটি শুধু কবিতা ও কল্পনার নয়, বরং সৃষ্টিশীলতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার প্রতীক।
১৯১৭ সালের ১০ জানুয়ারি ওমাহায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতার পাশাপাশি একটি মুদ্রণযন্ত্রের অর্ডার দেন বার্নহাট ব্রাদার্স কোম্পানিকে। এর দাম পড়ে ৫৪০ ডলার। তবে এটি পাঠাতে দেরি হয়, আর এপ্রিলেই আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মুদ্রণযন্ত্রটি ১০ জুলাই জাহাজে পাঠানো হয়, কিন্তু এর ব্যবস্থাপনায় সমস্যায় পড়েন রবীন্দ্রনাথ। যদুনাথ সরকারকে লেখা চিঠিতে তিনি জানতে চান, "চালাই কি করিয়া?" প্রেসটি ছেলেদের শিক্ষা ও আমোদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল, তবে তার খরচ মেটানোর জন্য সমাধান খুঁজছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ চেষ্টারত ছিলেন প্রেসটিকে লাভজনকভাবে ব্যবহারের জন্য। চিন্তামণি ঘোষকে দায়িত্ব নিতে বললেও তিনি অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে বিশ্বগ্রন্থপ্রকাশ নামে একটি উদ্যোগের পরিকল্পনা করেন, যেখানে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে ৫২টি গ্রন্থ প্রকাশের কথা ছিল। এসব বইয়ের কপিরাইট কিনতে লেখকদের ২০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। তবে মুদ্রণের জন্য সরকারের অনুমতি পেতে দেরি হয়, আর প্রেস অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।
ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এক সময় প্রেসটি লিংকনে ফেরত পাঠানোর কথাও ভাবেন। ৬ মার্চ ১৯১৮-এ পিয়র্সনকে লেখেন, "কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করব, তারপর প্রেসটি ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেব।" শেষ পর্যন্ত জুনে সরকারের অনুমতি মেলে এবং প্রেস চালু হয়। মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সুকুমার রায়সহ অন্যান্য অভিজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয়। সুকুমার ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোলপুরে এসে প্রেসের দায়িত্ব নেওয়ার পরিকল্পনা করেন।
এই পুরো প্রক্রিয়াটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রন্থপ্রকাশ ও শিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে।
শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত বই ছিল রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশটি গান নিয়ে সংকলিত গীত-পঞ্চাশিকা, যা ১৯১৮ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরলিপি সংযোজিত এই গ্রন্থটি ১২৪ পৃষ্ঠার, মুদ্রণ করেন জগদানন্দ রায়, এবং প্রকাশক ছিলেন চিন্তামণি ঘোষ। যদিও চিন্তামণি প্রেসের ভার নিতে ব্যর্থ হন, তবুও আশ্রমে বইটি মুদ্রণ করার মাধ্যমে প্রেসটি সচল হয় এবং কিছু অর্থ সঞ্চয় হয়।
পরবর্তীতে Selected Passages for Translation from English into Bengali এবং রবীন্দ্রনাথের The Fugitive বইও শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, এই প্রেসে মুদ্রণের ত্রুটিগুলোই তার স্থানীয়তাকে প্রমাণ করে। এতে সুকুমার রায় নিমাই ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়।
১৯১৮ সালের আশ্বিন মাসেই রবীন্দ্রনাথ গুজরাতি ব্যবসায়ীদের সামনে বিশ্বভারতী পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ৮ পৌষ ১৩২৫-এ। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ‘পাখি আমার নীড়ের পাখি’ গানটি ও তাঁর শিক্ষাদর্শ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি প্রস্তাব করেন, আদর্শ বিদ্যালয় হবে চাষাবাদ, গো-পালন, কাপড় বোনা এবং সমবায়ের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকদের জীবিকার যোগসূত্র স্থাপনের কেন্দ্র।
এই কর্মযজ্ঞে মুদ্রণ ও দপ্তরি কাজও যুক্ত ছিল। নিমাই, বিষ্ণু, এবং বাঁধাই শেখা সাঁওতাল ছাত্রদের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রামানন্দ প্রমুখের লেখার পাশাপাশি প্রেসের নতুন ম্যানেজার কালাচাঁদ দালালের কবিতা প্রকাশিত হয়, যা কবির আশীর্বাদও পেয়েছিল। এই প্রেসই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।
শান্তিনিকেতন প্রেসের কার্যক্রম ক্রমাগত উন্নত ও বিস্তৃত হচ্ছিল। বৈশাখ ১৩২৬-এ মুদ্রিত হয় দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি সম্বলিত রবীন্দ্রনাথের গীতি-বীথিকা, যা স্বরলিপি মুদ্রণের জটিলতায় প্রেসের দক্ষতা প্রমাণ করে। মাঘ ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয় নাটক অরূপরতন, যার জটিল পৃষ্ঠাবিন্যাসও প্রেসের সামর্থ্যের উদাহরণ।
অগ্রহায়ণ ১৩২৬-এ প্রেসে আরেকটি বড় মেশিন যোগ হয়, যার মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ শুরু হয়। একই সময়ে ঘোষিত হয় যে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর মুখপত্র হিসেবে প্রতিমাসে প্রকাশিত হবে। প্রেসের আর্থিক অবস্থাও উন্নত হয়—১৩২৬ থেকে ১৩২৭ পর্যন্ত আট মাসে লাভ হয় প্রায় ৭৫৪ টাকা।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা বইগুলির স্বত্ব বিশ্বভারতীর হাতে তুলে দেন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে উপার্জন বাড়ানোর পরিকল্পনা করেন। চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রকাশনার দায়িত্ব শান্তিনিকেতন প্রেসে স্থানান্তর করেন। ১৩৩০ সালে এক গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি গঠিত হয়, যেখানে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশসহ অনেকে যুক্ত ছিলেন।
পরবর্তীতে প্রেসে যোগ হয় নতুন যন্ত্রপাতি, যার মধ্যে ছিল রেকর্ড মেশিন, পেইন মেশিন, এবং ট্রেডল মেশিন। সুরেন্দ্রনাথ কর লন্ডন থেকে বাঁধাই ও লিথোগ্রাফি শিখে আসেন এবং সেই অভিজ্ঞতা প্রেসে প্রয়োগ করেন। নতুন যন্ত্র ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রেসের কার্যক্রম আরও সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকে, যার উল্লেখ শান্তিনিকেতন পত্রিকার ১৩৩০ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় পাওয়া যায়।
এই পুরো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শান্তিনিকেতন প্রেস কেবল মুদ্রণ নয়, বরং সাহিত্য ও সৃজনশীলতার একটি নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে।
১৯১৯ সালের নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের উত্তরের খোলা প্রান্তরে মাটির বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। মাথার চাল ছিল খড়ের, দরজা-জানালা দরমার, আর ঘরের মেঝে কাঁকরের পেটানো। শুধু স্নানের ঘরের মেঝে ছিল পাকা। প্রকৃতির মাঝেই ছিল তাঁর এই নতুন বাসস্থান।
এই বাড়ির চারপাশ ছিল খোলা আকাশ ও মাঠে ঘেরা, তবে রবীন্দ্রনাথের চোখের অবসর ছিল না। ১১ ডিসেম্বর ১৯১৯-এ রাণু অধিকারীকে লেখা চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, কাজ বন্ধ করে দিগন্তে চেয়ে থাকা তাঁর তীব্র ইচ্ছার কথা। পরে এই বাড়ির নাম হয় ‘কোণার্ক,’ যার দাওয়াতে ১৯১৬ সালে উপহার পাওয়া লিংকন প্রেসটি স্থাপন করা হয়। প্রেসটি তখন নীরব, যেমন নীরব ছিলেন কবি। যন্ত্র ও কবি দুজনেই তখন যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে, এক অখণ্ড নির্জনতায় ডুবে।
তবু, এই নীরবতার মাঝেও শান্তিনিকেতন প্রেস সচল ছিল, আর রবীন্দ্রনাথের বই একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে। কবির সৃষ্টিশীলতা আর প্রেসের কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতা তাঁর জীবন ও কর্মের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে থাকে।
গ্রন্থ: রামকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'কবির ছাপাখানা কবির প্রকাশনা’ অবলম্বনে।